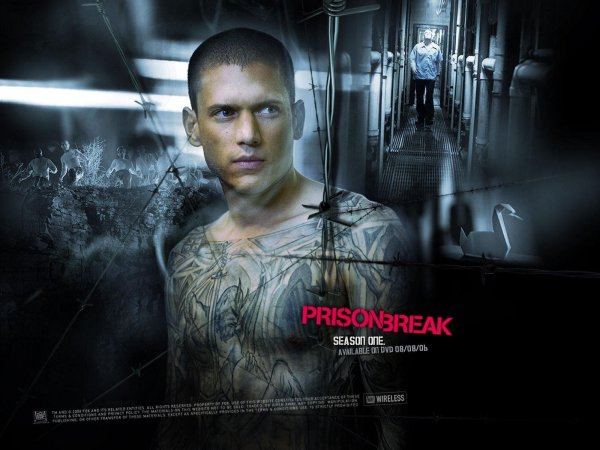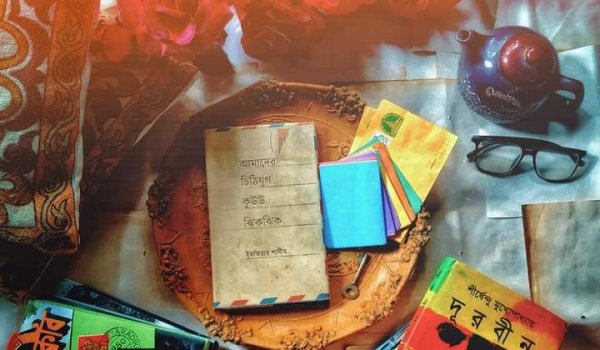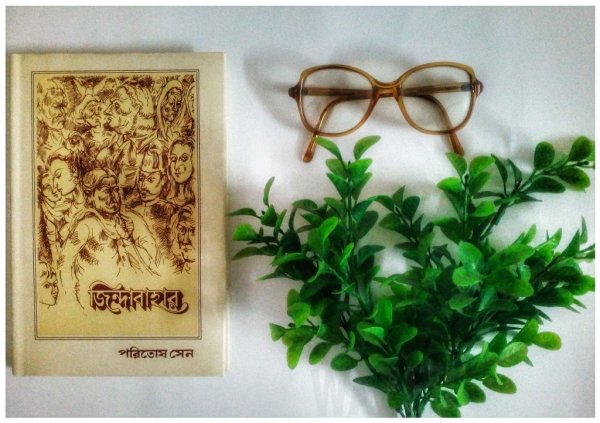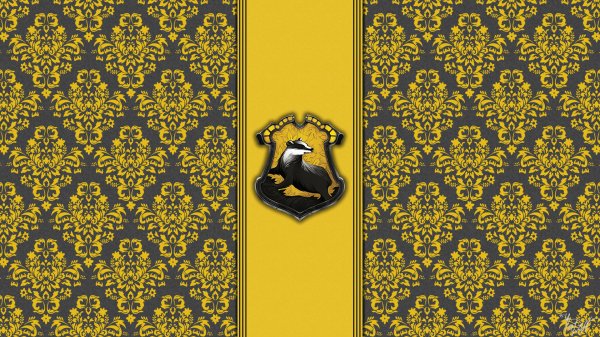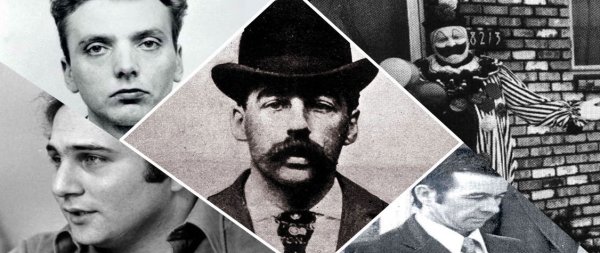দুটো চরিত্র, একটা লোকেশন এবং দুই ঘণ্টার বিরতিহীন গেইম। হুডানইট (কে এটা করল?) নয়, বরং হুডানহোয়াট (কে কী করল?) জনরার সিনেমা। ‘স্লিউথ’ নিয়ে সংক্ষেপে ধারণা দিতে হলে এধরনের ‘ক্যাচি’ লাইন ব্যবহার করতে হয়। তবে স্লিউথের গ্রেটনেসে তাতে কিছুমাত্র ভাটা পড়ে না। এমন সেটিংয়ের সিনেমা তো এর মুক্তি পরবর্তী সময়ে বেশ দেখা গেছে। তবে ওগুলো সিনেমা হয়েও নিপুণভাবে থিয়েট্রিক্যাল হতে পেরেছে কমই। তাও আড়ষ্টতাবিহীন। ‘স্লিউথ’ শব্দটির বাংলা অর্থ ‘গোয়েন্দা’ কিংবা চলতি ইংরেজি ‘ডিটেকটিভ’। এটি মূলত অ্যান্থনি শাফারের লেখা মঞ্চনাটক। তা সিনেমার চিত্রনাট্যে রূপান্তরিতও করেছেন তিনি। মঞ্চকে ছেড়ে নয়, বরং মঞ্চের মজ্জাতে থেকেই গর্বিতভাবে সিনেম্যাটিক হয়ে উঠেছে মাস্টার পরিচালক জোসেফ এল. মানকিউইকজে্র এই সিনেমা।
শুরুটাই তো হয় ‘ফোরশ্যাডোয়িং’ টেকনিকের সুচতুর ব্যবহার করে। নাম ক্রেডিটের বিভিন্ন চিত্র, সিনেমার পরবর্তী বিভিন্ন দৃশ্যেরই প্রতিরূপ। প্রারম্ভিক দৃশ্যেই দেখা যায়, সিনেমার প্রধান একটি চরিত্র ঢুকে পড়েন ছোট ছোট গাছ দিয়ে নির্মিত বেড়া দিয়ে ঘেরা এক গোলকধাঁধায়। কোনোমতেই কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারছেন না তিনি। ক্যামেরাও ট্র্যাকিং শটে অনুসরণ করছে তাকে। আরেকটি শটে কেন্দ্রে বসে আছেন সফল, জনপ্রিয় ক্রাইম-থ্রিলার ঔপন্যাসিক এন্ড্রু ওয়াইক। গোলকধাঁধার কেন্দ্রে তিনি রেকর্ড করছেন তার পরবর্তী ডিটেকটিভ থ্রিলার উপন্যাসের গল্প। নাকি এখানেও লুকিয়ে আছে আরেকটা ফোরশ্যাডোয়িং! সেই তরুণকে ধাঁধা থেকে বের করে আনেন এন্ড্রু ওয়াইক। এবং টপ শটে গোটা গোলকধাঁধাটা তখনই দেখতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্যটাই বলে দেয়, এন্ড্রুর নেমন্তন্নে আসা এই তরুণের ভবিতব্যে কী ঘটতে যাচ্ছে।
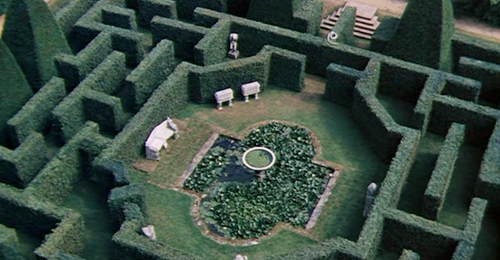
Image Source: Palomar Pictures International
তরুণ আসলে সম্ভ্রান্ত এই ইংরেজ এন্ড্রু ওয়াইকের স্ত্রীর প্রেমিক। পেশায় হেয়ারড্রেসার। নাম মাইলো টিন্ডল। ওয়াইক তাকে দাওয়াত করে এনে শুরু থেকেই একটা মারমুখী আচরণ দিয়ে কোণঠাসা করে রাখে। তার এই গোটা বাড়িটাই নানারকম বিভ্রান্তিজনক জটিল গেইম আর অটোমাটায় ভরা। মুহূর্তে মুহূর্তে মাইলোকে সে এসব দিয়ে নাস্তানাবুদ করে। মাইলোকে মূলত সে ডেকেছে, তার স্ত্রীর ভরণপোষণ সামান্য এই হেয়ারড্রেসার প্রেমিক কতটুকু করতে পারবে, তা যাচাই করতে। তবে প্রেমিককে বড় ধাক্কাটা ওয়াইক একটু পরেই দেয়। সরাসরি প্রস্তাব করে, তার স্টাডিরুমের সেইফে থাকা স্বর্ণালংকার চুরি করতে! লোকালয় থেকে বেশ দূরে এই জমিদারি। কারো দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই। চুরি করলে মাইলো পাবে হাজারো পাউন্ড।
আর চুরির ঘটনা দেখিয়ে এন্ড্রু পাবে ইন্স্যুরেন্সের টাকা। মাইলো হতভম্ব হয়। সে রাজি হয় না। কিন্তু এন্ড্রু তাকে ক্রমাগত ম্যানুপুলেট করতে থাকে। এটাই যে তার কাজ। থ্রিলার উপন্যাসে পাঠককেও তো সে এভাবেই ম্যানুপুলেট করে। এটা পুরোটাই তার কাছে একটা গল্পের প্লট। তার সারা বাড়িতে ছড়িয়ে থাকা গেইমের মতোই আরেকটা গেইম। মাইলো সবসময় মুখোমুখি হয়েছে জীবনসংগ্রামের। বাবা ছিল ঘড়ির মিস্ত্রী। কষ্ট, অভাব তার নিত্যসঙ্গী। এখন কিছুটা উন্নতি করেছে, কিন্তু প্রেমিকা মার্গারেটকে নিয়ে সুখে থাকতে হলে অনেক টাকা তার দরকার। প্রাক্তন স্বামী এন্ড্রু যে এতদিন পেলেপুষে বিলাসী করে তুলেছে মার্গারেটকে। বউকে কে নিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে অবশ্য সে চিন্তিত নয়। তার কাছে যৌন সম্পর্কটাই মূল, বিয়েটা এর ক্ষতিপূরণ মাত্র। যৌনতা, জীবন, মৃত্যু সবকিছুই একেকটা খেলা এন্ড্রুর কাছে।
মাইলো, এন্ড্রুর চুরির পরিকল্পনায় বাঁধা পড়ে যায়। কিন্তু সে জানে না, পুরোটাই তাকে অপদস্থ করার একটা ফাঁদ। একজন নাকউঁচু ব্রিটিশ এলিটিস্টের স্ত্রীকে প্রেমের তীরে ঘায়েল করার দুঃসাহসে নিচুশ্রেণির হেয়ারড্রেসারকে একটা শিক্ষা দেবে; এটাই মূল উদ্দেশ্য এন্ড্রুর। সোজা কথায়, মাইলোকে সে তার অবস্থান চেনাবে। এসব মাইলো জানতে পারে, এন্ড্রুর পরিকল্পনামতো নিখুঁত চুরি সম্পন্ন করার পর। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে এতক্ষণ চলা খেলার ইতিবৃত্ত জানিয়ে কার্তুজ শেষ করে এন্ড্রু ওয়াইক! গেইম কি তবে এখানেই শেষ?
গল্প যায় দিন কয়েক পরে। তদন্ত করতে ইন্সপেক্টর আসে। ওয়াইক চায় ধামাচাপা দিতে। তবে শেষ অব্দি স্বীকার করে, হয়নি কোনো হত্যা। পুরোটাই সাজানো পরিকল্পনা। ভুলে গেলে চলবে না, সে যেমন গেইমপ্লেয়ার; মাইলোও তেমন। শুধু তাদের খেলার পদ্ধতি ভিন্ন। শ্রেণিগত কারণে সারাজীবন অপমান আর বৈষম্যের শিকার হওয়া মাইলোর কাছে গেইম হলো রূপান্তরের নতুন অধ্যায়। তাই সে উঠতে পারে নীতিবিবর্জিত, বিপদজনক। নিজের মারপ্যাঁচে এন্ড্রুই পড়ে।
চালগুলো এবার আরো ধূর্ত আর তড়িৎ। তার অটোমাটাগুলো হাসছে তারই উপর। আরো একটা গেইম। দুই অঙ্কে গেইমের দুটো অধ্যায় শেষ। তৃতীয় অঙ্কের প্রবেশ। এবার যুক্ত হয় সত্যিকারের হত্যাকাণ্ড। গেইম শুধু গেইম নয়, হয়ে উঠেছে যার যার শ্রেণিজয়ের হাতিয়ার। দু’ ঘণ্টার এই বিরতিহীন খেলায় শেষ হাসিটা হাসবে তবে কে?

Image Source: Palomar Pictures International
‘স্লিউথ’ (১৯৭২) কখনো শেষে কে জিতল কিংবা হাসল, তা নিয়ে নয়। বরং শেষে পৌঁছানোর এই গোটা প্রক্রিয়াটিকে অভিঘাতী করে তোলাই সিনেমার মূল লক্ষ্য। শ্রেণিভিত্তিক দ্বন্দ্বকে গভীরতম ব্যক্তিগত স্তরে নামিয়ে খেলাটাই এখানে মুখ্য। শ্রেণিসচেতন দুই পুরুষের ডুয়েলটাই সিনেমার আসল মাংসল অংশ। তাদের মানসিক সক্ষমতাকে, বুদ্ধির খেলাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, দু’জনকে আগ্রাসী করার মাঝেই স্লিউথের সূক্ষ্ম রসবোধ যুক্ত আছে। সেইসাথে রহস্য ঘরানার দুর্দান্ত স্পর্শও রয়েছে।
পুরোপুরি চরিত্রনির্ভর সিনেমা এটি। দুটো চরিত্রই তো আছে আসলে। তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াতেই সকল কিছু। এক্ষেত্রে দর্শককে ধরে রাখা এবং বিস্ময়ের মধ্যে রেখে এগিয়ে নেওয়ার কাজটা অত্যন্ত কঠিন। এবং সেটা সহজাতভাবেই করতে পেরেছে নিজের মঞ্চনাটকের আদলে লেখা অ্যান্থনি শাফারের এই চিত্রনাট্য, যেটি অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত এবং বলাই বাহুল্য, ন্যারেটিভের প্রত্যেক বাঁকেই আছে অপ্রত্যাশিত কিছু। চরিত্রগুলোর নিখুঁত গঠন দেখে মনে হয়েছে, তাদের আচরণ নিয়ে, বৈশিষ্ট্য নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করা হয়েছে। উপাদানের প্রাচুর্য আছে দুটো চরিত্রেই। একদম স্বকীয় দু’জনেই।
তবে, একটা সিঙ্গেল লোকেশন আর দুই চরিত্র দিয়ে মঞ্চ ন্যারেটিভের এই সিনেমা গ্রেট হয়ে ওঠার পেছনে ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করছে দুই প্রথিতযশা অভিনয়শিল্পী লরেন্স অলিভিয়েই আর মাইকেল কেইনের অভিনয়। তাদের কারণেই স্লিউথে যোগ হয়েছে ‘রিপিট ওয়াচিং ভ্যালু’। দু’জনের ক্যারিয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র এবং চরিত্রাভিনয়; উভয়ই এ সিনেমায় পাওয়া গেছে। এন্ড্রু ওয়াইকের চরিত্রটা কোনোভাবেই পছন্দসই চরিত্র নয়। সে পথে চরিত্রটিকে বিন্যাসও করা হয়নি। কিন্তু অলিভিয়েইর অভিনয়ের ফলে দর্শক বুঝতে সক্ষম হয় এই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব। তার দ্বন্দ্ব, তার অহম, তার ভেঙে পড়া; সবকিছুই আলাদা আলাদাভাবে ধরতে পারে দর্শক।
ওদিকে মাইকেল কেইনের অনবদ্য অভিনয়ের ফলে মাইলো চরিত্রটির লড়াই, অপমানিত হবার কষ্ট, এমনকি তার ভেতরে ফুঁসে ওঠা সেই ক্রোধাগ্নিও বৈধতা পায় দর্শকের অন্তরে। মাইলোর রূপান্তরকে খুব কাছ থেকে দেখতে পায় দর্শক। অসাধারণ সব সংলাপ অলিভিয়েইর চরিত্র পেলেও, কেইনের চরিত্রটি যেন সংলাপ ছাড়াই শরীরী অভিনয়ের সবটা দেখানোর সুযোগ পেয়েছে অনেক দৃশ্যে। অভিনয়ের যে পরিমিতিবোধ, মাইলো চরিত্রটি দিয়ে তার এক অনন্য নজির উপস্থাপন করেছেন কেইন।

Image Source: Palomar Pictures International
তবে এতকিছুর পরেও, স্লিউথের যে ‘গ্রেট’ কিংবা ‘ক্লাসিক’ মর্যাদা; তা জোসেফ এল. মানকিউইকজে্র এমন পরিচালনা ছাড়া সম্ভব হতো না। ‘আ লেটার টু থ্রি ওয়াইভস’ (১৯৪৯), ‘অল অ্যাবাউট ইভ’ (১৯৫০)-এর মতো ক্লাসিক সিনেমা উপহার দেওয়া পরিচালকের মৃত্যুর আগে সর্বশেষ কাজ এটি। এর থেকে স্মরণীয় সমাপ্তি বোধহয় আর হয় না। এই সিনেমার যে থিয়েট্রিক্যাল স্টাইল, তা আসলে মানকিউইকজে্রই নিজস্ব শৈলী। ‘থিয়েটার দ্যু ফিল্ম’; এই ব্যক্তিগত জনরাটি তারই তৈরি এবং অনন্য শৈলী দিয়ে তিনিই নিখুঁত করে তুলেছেন।
মানুষের চেতনা, মানবিকতা নিয়ে তিনি বরাবরই কৌতূহলী। তার চরিত্রগুলোও তাই সবসময় স্বীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকে। মানুষকে তথা চরিত্রকে আরো কাছ থেকে, আরো গভীরভাবে দেখবেন বলেই তার এই জনরার সৃষ্টি। সংলাপ, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, ভিজ্যুয়াল; তিনটাই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ মানকিউইকজে্র ‘থিয়েটার দ্যু-ফিল্ম’ জনরায়। ট্যাগ গালাঘার যেমন বলেছিলেন,
“মানকিউইকজে্র সিনেমা আসলে অনেকটা মঞ্চকে ক্যামেরায় ধারণ করা।”
সেকথারই সফল এবং সবচেয়ে অমোঘ উদাহারণ এই ‘স্লিউথ’।
মানকিউইকজে্র শেষ এই সিনেমাতে তাঁর নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলীর সবকিছুই স্থান পেয়েছে। শ্রেণি সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব, পুরুষের প্রকৃতি, মঞ্চের আমেজের মাঝেও ক্যামেরায় সিন ব্লকিং আর শট কম্পোজিশনে একটা গীতিময়তা ধরে রাখা; সবকিছুরই নিখুঁত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় স্লিউথে। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয়, মানকিউইকজ্ সবসময় একদম আড়ম্বরহীন জায়গায় সবচেয়ে অভিঘাতী দ্বন্দ্বগুলোকে ধারণ করেন। সে জায়গায় সেটিং’য়ের কারণে ‘স্লিউথ’ সম্পূর্ণটাই, না চাইতে তেমন হয়েছে।
মঞ্চের ভাবটা এ সিনেমায় প্রকট থাকায় সম্পাদনায় কুইক কাট ব্যবহার করে সিনেম্যাটিক কড়চা যোগ করেছেন তিনি। ‘মিজ অ-সেন’ এর ব্যবহারটাও হয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত। সাসপেন্স বাড়াতে সাহায্য করেছে। কুশলী প্রোডাকশন ডিজাইনে অটোমাটাগুলোর ঠিকঠাক অবস্থানটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সিনেমায়। কুইক কাট ব্যবহার করে সেগুলোর ক্লোজআপ শট এ সিনেমার ভিজ্যুয়াল উইটের জায়গাটাকে পরিষ্কার করে তুলেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওগুলো আসলে জান্তব কিছু, যারা কখনো নিশ্চুপ কিংবা কখনো হেসে উঠে এই দুই পুরুষের শ্রেণি আর অহমের লড়াই দেখছে। এই চেনাজানা ডিভাইস যে সুনিপুণ ব্যবহারে দৃশ্যে অন্য মাত্রা যোগ করতে পারে, এই সিনেমা সেটার সুযোগ্য উদাহারণ।

Image Source: Palomar Pictures International
স্লিউথ’কে মানকিউইকজে্র আরেকটি গ্রেট সিনেমা ‘আ লেটার টু থ্রি ওয়াইভস’ (১৯৪৯)-এর অন্যপ্রান্তে রাখা যায়। সেখানে তিনটি নারী চরিত্র দিয়ে তিনি শ্রেণি সংগ্রাম নিয়ে তার নিজস্ব চেতনার উপর আলো ফেলেছিলেন। আর এখানে সেটা রূপান্তর হয়েছে দুই পুরুষের মধ্যে। এবং আরো গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে। তবে শেষ অব্দি, ‘স্লিউথ’ হয়ে উঠেছে একদম স্বকীয়। শেক্সপিয়রিয়ান ট্র্যাজেডির ধাঁচে চিরন্তন শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের এক অনন্য চিত্র হয়েছে সমাপ্তিতে। একইসাথে পরিচালক জোসেফ এল. মানকিউইকজে্র জন্য এটি একটি ‘পারফেক্ট ফেয়ারওয়েল’।