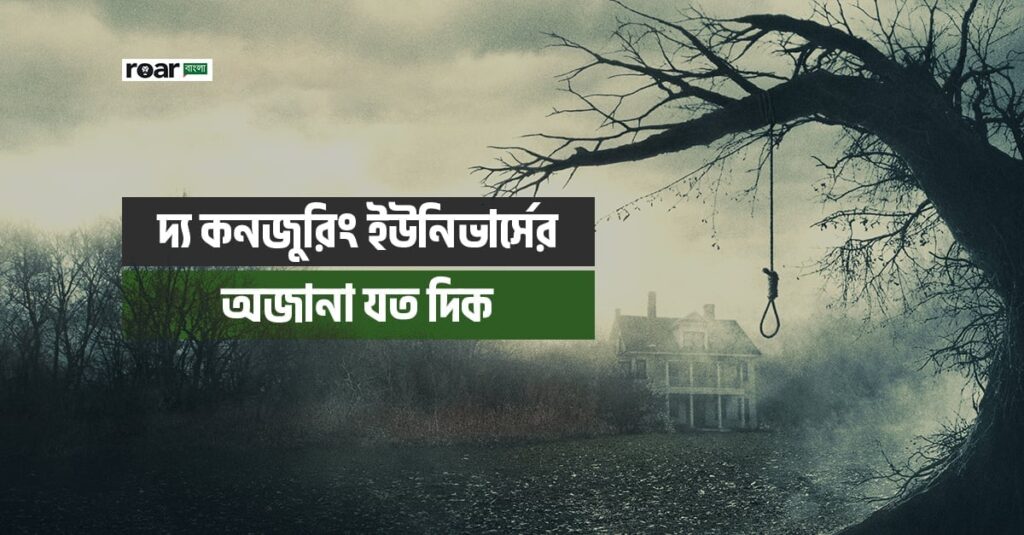১৯৩৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। বর্তমান বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার মাইজপাড়া গ্রামের স্কুল শিক্ষক কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গৃহিণী মীরা গঙ্গোপাধ্যায়ের কোল আলো করে জন্ম নেয় তাদের প্রথম সন্তান। তৎকালীন বাংলাদেশ: সবুজ বৃক্ষরাজি, দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ আর এঁকেবেঁকে ছুটে চলা অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদী- এই তার নিত্যকার রূপ! বাংলার এই অনিন্দ্য সুন্দর আবহ গায়ে মেখে একটু একটু করে বড় হচ্ছে কালীপদ-মীরা দম্পতির প্রথম সন্তান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের ডামাডোল আর পৃথিবীব্যাপী চলছে হিটলারের উত্থান।
কালীপদ নিজে থাকতেন কলকাতায়, জীবিকার তাগিদে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। সেখানে স্কুলে পড়ান, টিউশন করান। মা, স্ত্রী, সন্তান থাকেন পূর্ব বাংলায়; যা কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কাছে ‘বাঙ্গাল মুল্লুক’। এই অঞ্চল কৃষি প্রধান। শিক্ষাদীক্ষার বালাই খুব একটা নেই এখানকার মুসলমান কৃষকদের মাঝে। অন্যদিকে সারা ভারতবর্ষের মতো এখানকার পরিবেশও সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পে ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। তাই নিজ পরিবারের সুরক্ষায় তিনি নিয়ে নিলেন জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। মাতৃভূমির আলো-বাতাস, জল-মাটি আর অসীম আকাশের আশ্রয় থেকে সপরিবারে জীবনের পাট গুটিয়ে নিলেন তিনি। স্থায়ীভাবে পাড়ি দিলেন কলকাতায়।
প্রথম পুত্র সুনীলের বয়স তখন চার। প্রকৃতি সবসময় উদার হয় না, কখনও কখনও হয় কৃপণ! বুকের মাঝে যে স্বপ্নের জাল বুনে বুক ভাসানো কান্নায় মাতৃভূমি ছেড়েছিলেন কালীপদ, তার সেই স্বপ্নও পূরণ হয়নি। যে মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কালীপদ কলকাতাকে আপন করেছিলেন, সেই কলকাতা তার স্বপ্ন পূরণ করেনি। প্রতিনিয়ত তাকে লড়াই করতে হয়েছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। তাই তো জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অকাতরে খাটতে হয়েছে তাকে।
স্বপ্নভঙ্গের তীব্র বিষাদ বুকে জড়িয়ে স্ত্রীসহ চার সন্তানকে পৃথিবীতে রেখে মাত্র পঞ্চাশ বা একান্ন বছর বয়সে অকালে প্রয়াত হন কালীপদ। নানা সমস্যায় ধুঁকতে থাকা পরিবারটি পতিত হয় গভীর খাদে। সুনীল, অনীল, অশোক, কণিকাকে নিয়ে মীরা গঙ্গোপাধ্যায় পড়েন অকূল পাথারে। সুনীলের পূর্ব-পশ্চিম-এ আমরা পড়েছি, ‘প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না’। গাঙ্গুলি পরিবারের ক্ষেত্রে এই উক্তি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

কালীপদ পৃথিবী ত্যাগ করার কিছুদিন যেতে না যেতেই তার বড় পুত্র সুনীল নিয়ে নেয় সংসারের ভার। একসময় বাউণ্ডুলেপনায় যে ছেলে নিজ জীবনের লক্ষ্যই হারাতে বসেছিল, সেই ছেলেটির কাঁধেই পড়ে মা আর তিন ভাইবোনকে কলকাতায় টিকিয়ে রাখার ভার। শুরু হয় তার দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় ছোটাছুটি। এঘর-ওঘর ছুটে যায় টিউশন করতে। সেই টিউশনের টাকায় চলে মায়ের ওষুধ, ভাইবোনদের খাওয়া-পরা ও পড়াশোনা।
যে মানুষের শিরাতেই বইছে বাউণ্ডুলেপনার রক্ত, সে মানুষ কি বৃক্ষের মতো স্থির হয়ে থাকতে পারে? টিউশনির ফাঁকেফাঁকেই চলল নাক ডোবানো আড্ডা, বাস্তবতা ভোলানো ভ্রমণ। সঙ্গী ভাস্কর দত্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, শঙ্খ ঘোষসহ আরও অনেকে।
মায়ের পড়ার নেশা ছিল। ছোটবেলায় এর-ওর লাইব্রেরি থেকে মায়ের জন্য চেয়ে-চিন্তে বই আনতো সুনীল। কোনো কোনো অলস বিকেলে কিছু করার না থাকলে নিজেই নিয়ে বসতো সে বই। এভাবেই বইয়ের সাথে ওর সখ্য। কলকাতায় আসার প্রথম দিকে পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুশ্চিন্তা ছিল নতুন পরিবেশে এসে দুষ্টুসঙ্গে মিশে কিশোর পুত্র নাকি আবার বখে যায়! সেজন্য তিনি পুত্রকে খুব একটা বাইরে বেরুতে দিতেন না। শুধু মুখে বারণ করলেই তো আর শুনবে না, তাই তিনি পুত্রকে মগ্ন করে দেন টেনিসনের কবিতা অনুবাদের কাজে। সেই প্রথম কবিতার সাথে শব্দ-বর্ণ নিয়ে শুরু হলো খেলা। দিন গিয়েছে, কবিতার সাথে সুনীলের সেই খেলা পরিণত হয়েছে ভালোবাসায়।
পিতা থাকতেই কবিতা লিখতেন, পিতার মৃত্যুর পর এদিক-ওদিক ছাপা হতে লাগল তার কবিতা। বিক্ষিপ্তভাবে আসতে লাগল সুনামও। তার জের ধরে ১৯৫৩ সালে বন্ধু দীপক মজুমদারের সাথে বের করলেন কাব্য পত্রিকা কৃত্তিবাস। দিন গিয়েছে, বেড়েছে কৃত্তিবাস-এর সুনাম। সেই সুনামের লোভে মৌমাছির মতো ছুটে আসতে লাগল কলকাতার নানা প্রান্তের অসংখ্য কবি। এসব বিখ্যাত-অবিখ্যাত কবিদের কবিতায় আরও বেশি সমৃদ্ধ হলো কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস ও তার কবিদের নিয়ে নানা কথা ছড়ালো সারা কলকাতার পাঠক মহলে। তাদের অপরিমেয় মদ্যপান, মধ্যরাতে সারা শহর চষে বেড়ানো, হুট-হাট করে বেরিয়ে পড়া ভারত ভ্রমণে- এসব মুগ্ধ করতো রোমাঞ্চ প্রিয় পাঠকদের।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা পাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নানা বইয়ে।
’৬৩-সালে কবি পল এঙ্গেল-এর আহবানে ‘ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম’-এ যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়ায় পাড়ি জমান সুনীল। সেখানে ছিলেন পুরো একবছর। থেকে গিয়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ ছিল। দেশে থাকতে তীব্র অভাব প্রত্যক্ষ করার পরও শুধু বাংলা ভাষায় লেখার টানে ’৬৪-তে ফিরে আসেন নিজ দেশে। আবার শুরু করেন লেখালেখি। কৃত্তিবাস চলছিল তার আপন গতিতে। সেই গতিতে শামিল হলেন এপার বাংলার কবি বেলাল চৌধুরীও। বেলাল চৌধুরী নামের এই যুবককে সুনীল চিনতেন ‘কুমির ব্যবসায়ী’ হিসেবে। মানুষ গরুর ব্যবসায় করে, ছাগলের ব্যবসায় করে। কিন্তু একটা ছেলে- যে কিনা কুমিরের ব্যবসায় করে, সে কি সাধারণ কেউ? এই ছিল বেলাল সম্পর্কে সুনীলের প্রাথমিক ধারণা।
দেশে ফেরার পর এই ‘অসাধারণ’ বেলাল চৌধুরী ও পুরনো-নতুন অনেক বন্ধুদের নিয়ে বাউণ্ডুলেপনা নবোদ্যমে শুরু করেন সুনীল। সমউদ্যমে চলছিল কবিতা লেখাও। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল কৃত্তিবাস-এর কবিদের কথা। নামে-বেনামে চিঠি আসতে শুরু করল তাদের কাছে। সুনীলের কাছেও আসে- স্বাতী নামের এক অভিজাত পাড়ার তরুণীর। দিনে দিনে দুজনার চিঠি চালাচালি বাড়ে৷ সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে দুজনের প্রতি দুজনার হৃদয়ে অনুভূতির মেঘ। ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষার ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সুনীলের সাথে এখানে-ওখানে দেখা করতে শুরু করেন স্বাতী। তাদের দুজনের পরিচয়ের প্রথম দিককার এক মজার অভিজ্ঞতার বর্ণনা স্বাতীর বয়ানে এরকম:
একদিন ক্লাস থেকে ময়দানে গিয়ে একটা ছোট কালভার্টে বসে আমরা দুজন গল্প করছি। হঠাৎ দুজন কনস্টেবল এসে আমাদের খুব বকাবকি করে বলল ওখানে নাকি বসা বারণ- হয় আমাদের ওদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে, আর নয়ত কিছু টাকা জরিমানা দিতে হবে, আমি তো ভয়ে, লজ্জায় আধমরা, সুনীল, যদিও কিছু ঘাবড়ে গেছে- সেটা আমারই জন্য- তবু বললেন, আমরা থানাতেই যাব, অন্যায় তো কিছু করিনি, চলুন৷ ঠিক সেই সময়েই কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। ওই আগের পুলিশ দু’টি ছিল নকল পুলিশ, গুণ্ডা, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।
সুনীলের সাথে লুকিয়ে-চুরিয়ে স্বাতীর দেখা করার কথা জেনে যায় স্বাতীর পরিবার। অন্য আর পাঁচটা পরিবারের মতো স্বাতীর পরিবারও বাধা দেয় তাকে। তাদের চোখে সুনীল চালচুলোহীন ‘দমদমের এক গুণ্ডা’। এই ‘গুণ্ডা’র সাথে স্বাতীর কিছুতেই যায় না! কিন্তু অনড় স্বাতী। গেলে সুনীলের সাথেই যাবে, নয়তো কারে সাথেই নয়!
সুনীলের জায়গা থেকে সুনীলও অনড়। স্বাতীর পরিবারের প্রতি তার ভাষ্য-
আপনাদের মেয়েকে অন্য কোথাও বিয়ে দিতে পারেন তো দেন। কিন্তু ও যদি আমাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে আমি করবই।
দুজনার অনড় অবস্থা দেখে স্বাতীর পরিবারের অহমিকার বরফ গলে। জয় হয় দুজনার ভালোবাসার।

ঈশ্বরে সুনীলের ভক্তি নেই। সুনীল আত্মস্বীকৃত নাস্তিক। বিয়ে করতে চান রেজিস্ট্রি করে। কিন্তু দুই পরিবারের জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় রীতি মেনেই বিয়ে করেন। সালটা তখন ১৯৬৭।
শুরু হয় দুজনার নতুন ভ্রমণ। পরিবার ছেড়ে অর্থাভাবে পর্যুদস্ত সুনীলের পরিবারে থাকতে লাগলেন স্বাতী। বিয়ের পর একটা পরিবর্তন এলো সুনীলের মাঝে। সেই পরিবর্তনটাও তিন-চার মাসের জন্য। সুনীল আবার ফিরে গেলেন তার বোহেমিয়ান জীবনে। কফি হাউজে আড্ডা দেওয়া, কবিতা লেখা, মদ্যপ অবস্থায় মধ্যরাতে ঘরে ফেরা চলতে লাগল। হয়তো কখনও কখনও রাগ-অভিমান করেছেন। কিন্তু, সুনীলের এত এত অসঙ্গতির পরও সুনীলকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনও ভাবেননি স্বাতী। এর মাঝে জন্ম নিলো তাদের একমাত্র সন্তান সৌভিক।
পরিবারে নতুন অতিথি এলো, ব্যয়ও বাড়ল। সুনীল পদ্যের পাশাপাশি গদ্য লেখাও বাড়িয়ে দেন। সাধারণত সুনীলের লেখার সময় শুরু হতো সকাল নয়টা থেকে। চলতো দুপুর অবধি। ব্যয় বহনের জন্য তখন সুনীল কখনও কখনও গভীর রাতেও লিখতেন।
এভাবেই সুনীলের ছায়া হয়ে তার জীবনের উত্থান ও যবনিকাপাত দুটিরই সবচেয়ে বড় সাক্ষী হয়ে রইলেন স্বাতী। স্বামী বাংলা সাহিত্যের নামজাদা লেখক। নানালোক নানা সময়ে এসে ভিড় করতো সুনীলের কাছে। সেই ভিড়ে কখনও পুলকিত হতেন স্বাতী, আবার কখনও কখনও নিজেকে মনে হতো অনাহূতও। সেই অম্লমধুর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বাতী তার স্বপ্ন না মায়া না ভ্রম বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন:
এমনও হয়েছে- সুনীলের সঙ্গে আলাপ করতে এসে কেউ কেউ আমারই বেশি বন্ধু হয়ে গেছেন- ছেলে বা মেয়ে যে-ই হোক। অবশ্য কখনও কখনও এমনও হয়েছে- অনুভব করেছি আমার উপস্থিতি এখানে অবাঞ্ছিত। কখনও কারও প্রশংসায় মনে হয়েছিল আমি যেন সুনীলের প্রশংসা নিজের বলে মনে করছি, এবং তাতেই ডগমগ। অনেকটা তুয়ার গরবে গরবিনি হাম। কথা হলো এইসব নিয়েই চলতে হবে, চলতে হচ্ছে। এইতো জীবন!
সুনীল মারা যান আটাত্তর বছর বয়সে। মৃত্যুর জন্য তখন অবধি মানসিক প্রস্তুতিও তার ছিল না। লেখার টেবিলে তার অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলো অন্তত তারই সাক্ষ্য দেয়।
তার অনেক কথা বলার ছিল, অনেক লেখা লেখার ছিল। সেই অব্যক্ত কথা ও লেখারই এক অসামান্য দলিল স্বাতীর স্বপ্ন না মায়া না ভ্রম। তাই, সুনীলপিপাসু পাঠকদের জন্য এই বই অবশ্য পাঠ্য একটি বই।
স্বপ্ন না মায়া না ভ্রম বইটি কিনতে ভিজিট করুন রকমারিতে।