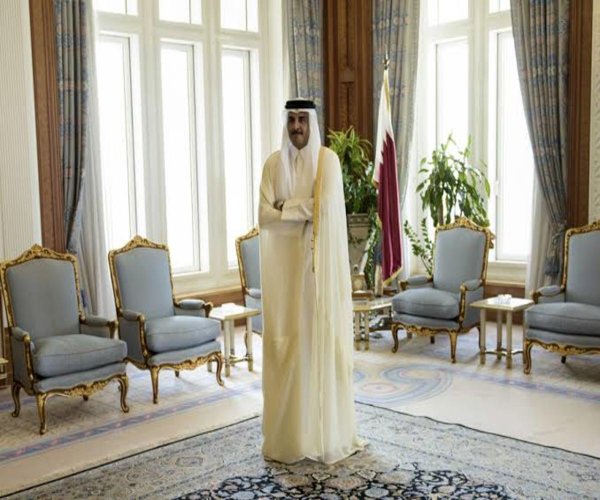আধুনিক গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় আটলান্টিক রেভ্যুলুশনের মাধ্যমে, শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পাড়ের দেশগুলোতে শুরু হয় গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বব্যাপী বাড়তে থাকে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা, অর্ধশতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে। নগররাষ্ট্রের যুগ থেকে শাসনতান্ত্রিক মতবাদ হিসেবে চর্চা হচ্ছে গণতন্ত্রের, একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।
মানুষের রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলো পরিচালিত হয় দুই ধরনের স্বার্থ দিয়ে। মানুষ মতাদর্শগত কারণে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়। অর্থনৈতিক স্বার্থও মানুষকে টেনে নিয়ে আসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। ফলে, শাসনতন্ত্র হিসেবে গণতন্ত্র আদর্শিক কারণে রাজনীতিতে যুক্ত থাকা মানুষদের কীভাবে সন্তুষ্ট করতে পারবে, সেটি সবসময়ই আলোচনায় থেকেছে গত শতাব্দীজুড়ে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ক্ষমতার ভারসাম্য আনে, সকল স্তরের রাজনৈতিক নেতৃত্বে এবং আমলাতন্ত্রকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে পারে, নাগরিকদের নিশ্চয়তা দেয় রাজনৈতিক অধিকার আর সিভিল লিবার্টির।

আবার, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, গণতান্ত্রিক শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশি হয় নাকি স্বৈরশাসকদের অধীনে বেশি হয়, সেই বিতর্ক বেশ জোরেশোরেই আলোচিত হচ্ছে এই শতাব্দীতে। বিশেষ করে চীনের অর্থনৈতিক উত্থান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কর্তৃত্ববাদী শাসকদের অর্থনৈতিক সাফল্য এই বিতর্ককে উসকে দিয়েছে। কর্তৃত্ববাদী শাসকদের অধীনে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে, অর্থনীতির আকার বড় হয়, বাড়ে মাথাপিছু আয়। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নবাদকে কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা ব্যবহার করে তাদের শাসনের ব্যাপারে নৈতিক বৈধতা অর্জন করতে, নাগরিকদের মধ্যে সন্তুষ্টির অনুভূতি তৈরি করতে। নাগরিকেরাও অর্থনৈতিক সাফল্যের বিনিময়ে রাজনৈতিক অধিকারগুলোর ব্যাপারে সমঝোতা করে, কর্তৃত্ববাদী সরকারকে দেয় যেকোনো কিছু করার অসীম স্বাধীনতা।
কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা কি আসলেই অর্থনৈতিকভাবে সফল?
চীন মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে শুরু করে ১৯৭৮ সালে। এরপর থেকে, চীন ধারাবাহিকভাবে ১০ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে, ৮০ কোটি মানুষকে বের করে নিয়ে এসেছে দারিদ্রসীমার নিচ থেকে। চীনে শিক্ষা খাতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, স্বাস্থ্যসেবার আধুনিকায়ন হয়েছে, বেড়েছে নগরায়নের হার। গত চার দশকে চীনে বিপুল অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে, রপ্তানি আয় বেড়েছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে চীন, কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে উত্থান ঘটেছে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে।

চীনের মতো অর্থনৈতিক সাফল্য পাচ্ছে ‘অনুদার গণতন্ত্র’ বিরাজ করা দেশগুলোও। অনুদার গণতন্ত্রের দেশগুলোতে সাধারণত ভোটাধিকার থাকে সীমিত পরিসরে, রাজনৈতিক অধিকারের সংকোচন ঘটে, নির্বাচন ম্যানুফেকচারিংয়ের ঘটনা ঘটে, সিভিল সোসাইটির প্রভাবকে সীমিত করা হয়, এনজিওগুলোর কাজের পরিধিকে কমিয়ে দেওয়া হয়। নিয়মিত নির্বাচন অনুদার গণতন্ত্রগুলোকে আয়োজিত হয়, কিন্তু ক্ষমতার পরিবর্তন হয় খুব কম ক্ষেত্রেই। রাজনৈতিক অধিকার আর সিভিল লিবার্টির এই সংকোচনের বিপরীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুক্তি দেখায় কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা। সাম্প্রতিক সময়ে চীনের অর্থনৈতিক উত্থান, আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিবর্তন আর কতৃত্ববাদী অন্যান্য দেশের উদাহরণের আলোকে বলা যায়, স্বৈরাচারী শাসকদের আমলে অর্থনীতি সচল থাকে, অবকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি ঘটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।
কেন অর্থনৈতিকভাবে সফল স্বৈরশাসকেরা?
প্রাচীনকালে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কিছু অংশে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা ছিল গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলোতে। অন্যদিকে, চীনে সুদূর অতীত থেকে শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি ছিল, শাসনব্যবস্থা ছিল নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক। কিন্তু, ইউরোপের রিপাবলিকগুলোর চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থানে ছিল চীন, একইরকম বাস্তবতা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও। বিভিন্ন কারণেই স্বৈরশাসকেরা অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।
প্রথমত, স্বৈরশাসনের অধীনে থাকলে রাষ্ট্র সাধারণভাবে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ি শ্রেণির সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের। অনেক সময় ব্যবসায়ী শ্রেণি থেকেই আসে রাষ্ট্রের মুখ্য নেতৃবৃন্দ। ফলে, রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে, কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণাকে উহ্য রেখে। অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে বিপুল বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে স্বৈরশাসকেরা, সকল রিসোর্স একসাথে করে এগিয়ে নেয় অবকাঠামোগত উন্নয়নকে। এটি অর্থনীতির আকারকে বড় করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রভাবিত করে ইতিবাচকভাবে।

দ্বিতীয়ত, স্বৈরশাসকেরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সংকটে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারেন, নিতে পারেন কার্যকর উদ্যোগ। ফলে, বন্যা, খরার মতো দূর্যোগগুলো থেকে দ্রুত রাষ্ট্রকে বের করে আনতে পারে স্বৈরশাসকেরা, দূর্যোগ কাঁটিয়ে রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন স্বাভাবিক জীবনে।
তৃতীয়ত, স্বৈরশাসকের অধীনে আমলাতন্ত্র এককেন্দ্রিক কাঠামো হিসেবে কাজ করে, সকল সিদ্ধান্ত নির্ভর একক ব্যক্তির উপর। ফলে, সিদ্ধান্ত প্রদানকারী স্বৈরশাসক দূরদর্শী উদ্যোগ নিতে পারলে, সেটি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। আবার, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকল সক্ষমতা একসাথে ব্যবহার করতে পারেন স্বৈরশাসক।
চতুর্থত, অনেক সময়ই প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি না ঘটলেও, স্বৈরশাসকেরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য মনগড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেন। আমলাতন্ত্রে নিজের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে মনগড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রদর্শন করেন, নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের মাধ্যমে ব্যবস্থা করেন সেই মনগড়া তথ্যের বিপুল প্রচারের। এজন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে অনেক সময়ই প্রবৃদ্ধির হারে পার্থক্য দেখা যায় কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে।

স্বৈরশাসকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ্রহণযোগ্যতা
চীনের মতো অনেক কর্তৃত্ববাদী দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে। মুয়াম্মার গাদ্দাফির শাসনামলজুড়ে লিবিয়াতে প্রবৃদ্ধি ছিল দুই ডিজিটের ঘরে, মিশরে হুসনি মোবারক আর ইয়েমেনের আলি আব্দুল্লাহ সালেহও সফল ছিলেন অর্থনৈতিকভাবে। কিন্তু, এই অর্থনৈতিক সাফল্যের গ্রহণযোগ্যতা সবসময়ই প্রশ্নবিদ্ধ থেকেছে।
প্রথমত, স্বৈরশাসক অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিকভাবে যত সফলই হোক, তার পতন আসেই। আধুনিক যুগে খুব কম স্বৈরশাসকই এক যুগের বেশি সময় টিকে থাকতে পেরেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক স্বৈরশাসককে প্রতিস্থাপন করেছে আরেক স্বৈরশাসককে। নতুন স্বৈরশাসকের উত্থানের বাইরেও, স্বৈরশাসনের আরো দুইটি ফলাফল আছে। গৃহযুদ্ধ ও দূর্ভিক্ষ। অর্থাৎ, যতো অর্থনৈতিক উন্নয়নই হোক এক স্বৈরশাসকের আমলে, সেটি গৃহযুদ্ধ বা দূর্ভিক্ষের মতো অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কারণে দীর্ঘমেয়াদে এসব অর্থনৈতিক অর্জনের কোনো গুরুত্ব নেই।

দ্বিতীয়ত, স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে অধিকাংশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হয় অবকাঠামোকে কেন্দ্র করে, শিক্ষা আর গবেষণার মতো জায়গাগুলোতে বিনিয়োগ থাকে অত্যন্ত কম। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ কম থাকায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ কম থাকে, যা বিশ্বায়নের যুগে যেকোনো দেশকে পেছনে ফেলতে পারে। মধ্যযুগের পুরোটা সময়জুড়ে ইউরোপের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থানে ছিল এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো। ভালো অবস্থানে ছিল মধ্যপ্রাচ্যও। কিন্তু, ইউরোপের শিল্পবিপ্লব পৃথিবীর রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সূত্রগুলোকে স্থায়ীভাবে বদলে দেয়। পৃথিবীর নেতৃত্বে নিয়ে আসে আটলান্টিক মহাসাগরের পাঁড়ের দেশগুলোকে, রাজনৈতিকি কর্তৃত্বের পাশাপাশি পৃথিবীজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব। অর্থাৎ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন স্বল্পমেয়াদে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত মানুষের সমর্থন অর্জন ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী কোনো প্রভাব রাখতে সক্ষম নয়, যা অর্থনীতির জন্য মোটাদাগে ইতিবাচক হবে।
তৃতীয়ত, স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অভিজাত শ্রেণি রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী জায়গাগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে, নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোকে সামনে রেখে। ফলে, অর্থনীতির আকার বড় হওয়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে ধনী আর দরিদ্রদের মধ্যে বৈষম্য। বিপুল পরিমাণ সম্পদ পূঞ্জীভূত হয় একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে। আইনের শাসন থাকে না, থাকে না সামাজিক ন্যায্যতার সুযোগ। এই রাজনৈতিক অনিয়ম সংঘাতকে উসকে দেয়।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রবৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্থ করে না
স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলোর অধীনে স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক সাফল্য আসলেও, দীর্ঘমেয়াদে সেই সাফল্য টিকে থাকে না, অর্থনৈতিক সাফল্যের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে। স্বল্পমেয়াদে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর অর্থনৈতিক অর্জনও স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলোর কাছাকাছি থাকে। তবে, গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা হলো, সেই প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকে, প্রবৃদ্ধির সুবিধা পৌঁছায় অর্থনৈতিক পিরামিডের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত। বাজারে জবাবদিহিতা আর ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারলে, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশ।