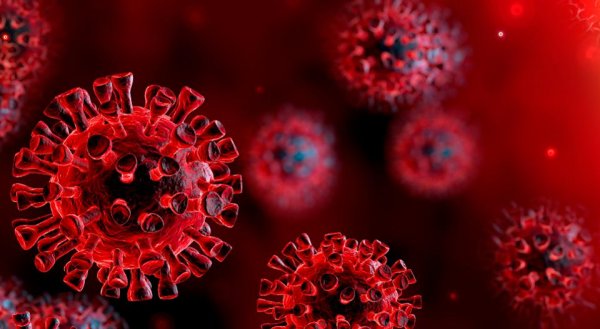একটি জাতিসত্তা বলতে আমরা কী বুঝি? একেবারে সাদামাটা ভাষায় কিছু নির্দিষ্ট মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ধর্মচর্চা, শিল্প-সংস্কৃতির বোধ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে মোটের ওপর যা কিছুর জন্য সেই মানুষগুলো অন্যদের থেকে আলাদা। একাধিক বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত রূপে যখন কিছু সংখ্যক মানুষের একটি দল নিজস্বতা অর্জন করে, তখন জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখার দায়ও তাদের ওপর বর্তায়, যেটি তারা স্বাভাবিকভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত করার আশা করে। একটি জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেয়ে ফলপ্রসূ কোনো পন্থা সম্ভবত আজ অবধি পৃথিবীর ইতিহাসে তৈরি হয়নি। একটি জাতির চেয়ে অন্য একটিকে উচ্চাসনে বসানোর যে প্রোপ্যাগান্ডা, তাকে সফল করার প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রথমোক্ত জাতির সংস্কৃতিবোধের মূলোৎপাটন করা।
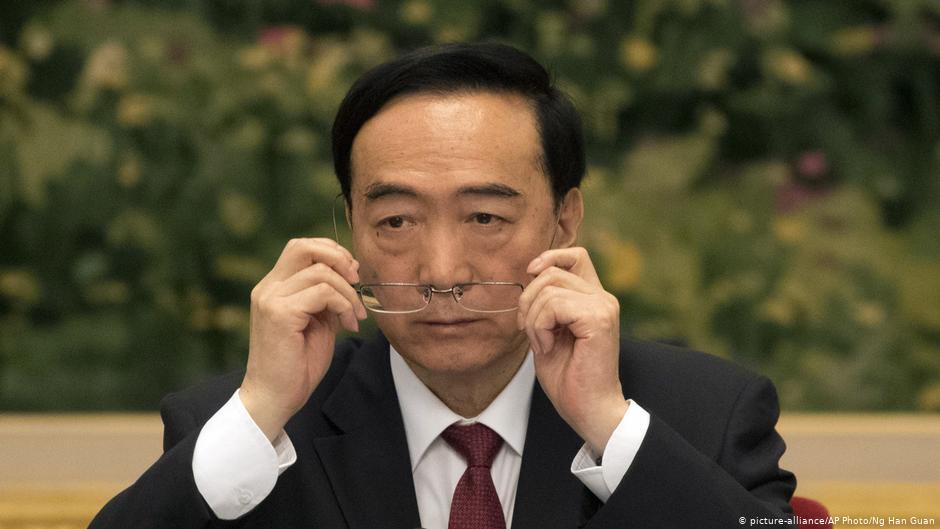
সময়ের সবচেয়ে আলোচিত সাংস্কৃতিক উচ্ছেদ ঘটছে চীনের উইঘুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে। চীন সরকারের একমাত্র লক্ষ্য সংখ্যালঘু এই জাতিকে চীনের মূলস্রোত হ্যান সম্প্রদায়ের সাথে একীভূত করে দেওয়া। চীন সরকার ইতোমধ্যেই ১,০০,০০০ উইঘুর সদস্যকে বিভিন্ন ক্যাম্পে অন্তরীণ করে রেখেছে। রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন, জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ, হরেক রকমের অত্যাচার- দেশটির সরকার কী চালাচ্ছে না এসব ক্যাম্পে!
চীন সরকারের উইঘুরকেন্দ্রিক এসব কার্যক্রম শুধু উইঘুরের অধিবাসীদেরকে নিয়েই নয়, বরং সরকারের খাস নির্দেশে উইঘুরদের অসংখ্য তীর্থস্থান এবং কবরস্থান পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। শিনজিয়াং-এর সমস্ত স্কুলে উইঘুর ভাষার ব্যবহার পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে- মান্দারিন ভাষার সর্বাত্মক প্রচার-প্রসার। উইঘুর সম্প্রদায়ের অধিকাংশের ধর্মীয় বিশ্বাস ইসলামচর্চাকে সরাসরি চরমপন্থী আচরণ বলে প্রচার করা হয়েছে। চীন সরকার তাদের এসব পদক্ষেপের কারণ হিসেবে দেখাচ্ছে- ধর্মীয় চরমপন্থী মনোভাবের বিকাশ রোধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী সকল দলের উত্থান রোধ, জঙ্গি নির্মূল ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে চীনের উদ্দেশ্য দিনের আলোর চেয়েও পরিষ্কার- জাতিগত বৈচিত্র্য ঘুচিয়ে দেশে একমাত্র সম্প্রদায় হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হ্যান সম্প্রদায়ের বিকাশ। উইঘুর সম্প্রদায়ের সকল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়বোধ লোপ করে হলেও তাদেরকে হ্যান সম্প্রদায়ের আদলে গড়ে তোলার প্রয়াস বস্তুত সাংস্কৃতিক গণহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উইঘুর জাতিসত্তার ওপর দেশটির সরকারের চালানো কর্মযজ্ঞ যেন অরওয়েলিয়ান বিভীষিকারই নামান্তর। শিক্ষাশিবিরে পাঠানো লাখ লাখ লোককে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে চীন সরকার নিযুক্ত করেছে বিশেষ কিছু কর্মকর্তাকে, যাদেরকে বলা হচ্ছে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সবচেয়ে চৌকস ও আধুনিক নাগরিক। রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপন করা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। প্রত্যেক উইঘুর নাগরিকের মুঠোফোনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে স্পাইওয়্যারের ব্যবহার, যাতে তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট সদা জাগ্রত থাকতে পারে।
পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া দেশটি বরাবরই রাষ্ট্রের কাছে উইঘুরের নাগরিকদের ন্যায়পরায়ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এসেছে। জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় উভয় কারণ দর্শানোর মাধ্যমেই তারা যে রাষ্ট্রের প্রতি প্রকৃতপক্ষে হুমকিস্বরূপ- এ কথা প্রতিষ্ঠা করতে চীন বদ্ধপরিকর। শুরু থেকেই বিবদমান সম্পর্ক আরও অবনতির দিকে এগোয় যখন ২০০৯ সালে উইঘুর সম্প্রদায় দাঙ্গা ও প্রতিশোধমূলক একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলাফল? হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষের স্রেফ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া।

উইঘুর সম্প্রদায়কে শক্ত হাতে দমন করার জন্য চীনের একমাত্র অজুহাত ইসলাম, যাকে সরকার আখ্যা দিয়েছে প্রবল সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে। এই ব্যাধির সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা হিসেবে চীন সরকার বেছে নিয়েছে সকল উইঘুরদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিন। ২০১৮ সালে চালু হওয়া ক্যাম্পগুলোর আকার ইতোমধ্যেই দ্বিগুণ হয়েছে। শিক্ষা শিবির থেকে ফেরত আসা উইঘুররা আর কখনোই স্বজনদের ফোন তুলছেন না- এমনটাই অভিযোগ করেছেন প্রবাসী উইঘুররা। বিদেশে বসবাসরত উইঘুররা এটুকুও জানতে পারছেন না যে শিক্ষা শিবির থেকে তাদের পরিবারের সদস্যরা আদৌ ফিরে আসছেন না শিক্ষা শিবির থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছেন অন্য অনেকের মতো।
উইঘুর মাত্রই সরকার কর্তৃক ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ ও ‘চরমপন্থী’ আখ্যা পাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে একধরনের অমানবিক আচরণ। যেকোনো উইঘুরকে (বিশেষত যুবক বয়সী কেউ) ঢালাওভাবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে দেশ ও জাতির প্রতি হুমকি হিসেবে, যাকে যেকোনো মূল্যে লোপাট করে দেওয়াই হচ্ছে চূড়ান্ত সমাধান। চীনের মতো একটি দেশ, যেখানে অনলাইনে নাগরিকদের গতিবিধিকে সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারির মাঝে রাখা হয়, সেখানে ইসলাম ও উইঘুর বিরোধী সকল মন্তব্য কোনো এক অজানা কারণে রাষ্ট্রের দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুত শিনজিয়াং-এর বাইরে উইঘুরদের বাস করাটা একপ্রকার অসম্ভবই হয়ে পড়েছে। অসংখ্য হ্যান সম্প্রদায়ভুক্ত চাইনিজদের আটক করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে- স্রেফ এই যুক্তিতে যে তারা উইঘুরদের বাসা ভাড়া দিয়েছেন!
সাংস্কৃতিক গণহত্যাকে প্রতিহত করতে হয় সংস্কৃতির মাধ্যমেই। প্রতিবাদের ভাষাও তাই একটাই- নিজস্ব সংস্কৃতির স্ফুরণ। শিল্প-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এমন কোনো হীরে-জহরত নয় যে তাকে সুরক্ষিত সিন্দুকে লুকিয়ে রাখলেই সে যুগ যুগ টিকে যাবে। শুধু কাগজে-কলমে অস্তিত্ব থাকলেই কোনো সংস্কৃতি বেঁচে থাকে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ল্যাডিনো ভাষার কথা। বর্তমানে প্রচলিত ও ব্যবহৃত ল্যাডিনো ভাষাটি স্প্যানিশ ভাষার মধ্যযুগীয় সংস্করণ ল্যাডিনোর সাথে তেমন সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। ল্যাডিনো নানা অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বদলে গেছে অনেকটাই। বর্তমান ল্যাডিনোতে রয়েছে অটোমান সাম্রাজ্যের শিল্প-সংস্কৃতির বহু উপাদান।
মূলত উইঘুর সম্প্রদায়ের সদস্যদের একই ধারা অনুসরণ করতে হবে। সংরক্ষণের নিমিত্তেই একে ছড়িয়ে দিতে হবে। উইঘুররা তাদের নিজেদের মধ্যে শুধু আবদ্ধ থাকলে তাদের সংস্কৃতির বিকাশ কখনোই হবে না। উইঘুর বলতে তারা কী বোঝে, নিজেদের কাছে তাদের পরিচয় কী, তাদের রুচিবোধ কী, ধর্মীয় বিশ্বাসকে তারা কীভাবে ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করে এসব কিছুই তাদের সারা বিশ্বের (নিদেনপক্ষে চীনের অন্যান্য অঞ্চল) সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এই কাজটি করার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে বিদেশে বসবাসরত উইঘুরদের। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের মূলত নিজেদের সংস্কৃতিকে বিশ্বের মাঝে বিস্তার লাভে উদ্যোগী হতে হবে। সরকার কর্তৃক সকল দমনমূলক নীতির অবসান ঘটানোর পাশাপাশি উইঘুররা আত্মপরিচয়ের বিকাশ ঘটালে বিদ্যমান পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়া শুরু করবে। রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে একাধিক অস্ত্র আছে, আর উইঘুরদের কাছে একটাই অস্ত্র- আত্মপরিচয়।

উইঘুরদের মাঝে একটি প্রবণতা কাজ করে তীব্রভাবে। সেটি হলো নিজেদের পরিশুদ্ধ ভাবা। সাংস্কৃতিক পরিচয় টিকিয়ে রাখার অর্থ এই না যে শুধু নিজের মতো করে বেঁচে থাকা। নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে আস্থাভাজন ও সমৃদ্ধ প্রমাণ করার উপায় হলো এগুলোর মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা। আমার এমন কিছু আছে যা দিয়ে আমি অন্যের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম- এই বিষয়টি যখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে, তখনই সাংস্কৃতিক স্থায়িত্বের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাবে উইঘুররা। উইঘুরদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ, উইঘুরদের বক্তব্যের প্রচার-প্রসার, তাদের খাদ্যাভ্যাস, বিভিন্ন ভাষায় তাদের সাহিত্যকর্মের অনুবাদ, উইঘুরদের নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি অন্য কোনো ভাষায় দখল ইত্যাদি বহুমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে উইঘুররা নিজেদের সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখতে পারে।