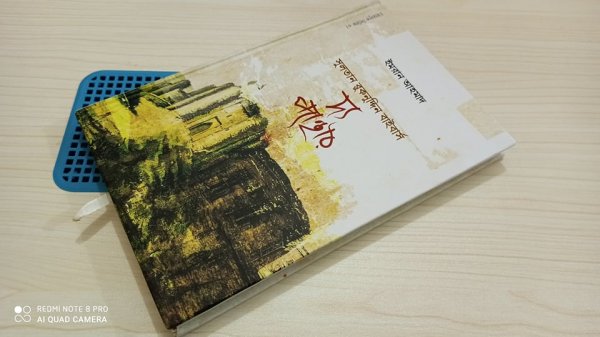“আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব যে, It is not an imaginary story, বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসি নি। …যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই থিসিসটা বুঝুন, সেটা সম্পূর্ণ সত্যি। সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি আপনাকে এলিয়েনেট করব প্রতি মুহূর্তে। যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, ছবি দেখে বাইরের সেই সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলের কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার প্রোটেস্টকে যদি আপনার মাঝে চারিয়ে দিতে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা।”
চলচ্চিত্রকে প্রতিবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার একটা মাধ্যম হিসেবে এভাবেই ভাবতেন ঋত্বিক ঘটক। সত্য বলার সেই দুরন্ত স্পর্ধা থেকে সারাটা জীবন যা ভেবেছেন তা নিয়েই নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র। পুঁজিবাদী সমাজে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লড়াইয়ের গল্পগুলো তিনি খুব সচেতনভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর চলচ্চিত্রগুলোতে।

১৯৫১ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণের যাত্রা শুরু হয় ঋত্বিক ঘটকের। প্রথম সিনেমা ‘বেদিনী’ মাঝপথেই অর্থাভাবে আটকে যায়। তবুও থেমে থাকেননি তিনি, নতুন গল্প ও চিত্রনাট্য নিয়ে শুরু করেন নতুন ছবি ‘অরূপ কথা’। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে প্রায় ২০ দিন ধরে শুটিং হয় এই চলচ্চিত্রের। কিন্তু ক্যামেরায় ত্রুটির জন্য প্রকাশ পায়নি এটিও। এরপর শুরু করেন ‘নাগরিক’ ছবির কাজ। কিন্তু আর্থিক কারণে তখন মুক্তি পায়নি এই চলচ্চিত্রটিও। ১৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে মুক্তি পায় ‘নাগরিক’। পর পর তিনটি অপ্রকাশিত চলচ্চিত্রের যন্ত্রণা নিয়ে থেমে যাননি ঋত্বিক। ১৯৫৮ সালে প্রথম মুক্তি পায় মানুষ ও যন্ত্রের প্রেম নিয়ে তাঁর চলচ্চিত্র ‘অযান্ত্রিক’। এভাবে পঞ্চাশ বছরের জীবনে বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তিনি নির্মাণ করতে পারেন মাত্র আটটি চলচ্চিত্র।
১৯৬০ সালের ১৪ এপ্রিল মুক্তি পায় ঋত্বিক ঘটকের চতুর্থ এবং প্রথম ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র ‘মেঘে ঢাকা তারা’। দেশভাগ পরবর্তী কলকাতায় এক নিম্ন মধ্যবিত্ত শরণার্থী পরিবারের সংগ্রামমুখর জীবন নিয়ে নির্মিত হয় এই চলচ্চিত্রটি। শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস থেকে ঋত্বিক ঘটক এর কাহিনী নেন।

পঞ্চাশের দশকে কলকাতা শহরের এক প্রান্তে রিফিউজি কলোনির একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরেই এর গল্পটি আবর্তিত। স্কুলশিক্ষক বাবা এবং গৃহিণী মায়ের সংসারের চার সন্তান- দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। এই চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র নীতা, পরিবারের বড় মেয়ে। তার বড় ভাই শংকর গায়ক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর, সংসারের অভাব অনটন নিয়ে সচেতন নয়। ছোট দুই ভাই বোন- মন্টু এবং গীতার মাঝে আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাদের মনোযোগ থাকে না। আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন স্কুলশিক্ষক বাবা। কাজেই সংসারের পুরো ভার এসে পড়ে নীতার কাঁধে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সবার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার এক প্রাণান্তকর লড়াইয়ে নামতে হয় তাকে। এরপর ঘটে যায় অনেক কিছু। নীতার প্রেমিক সনৎ তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিয়ে করে তার ছোট বোন গীতাকে, বড় ভাই শংকর এই ঘটনায় বেদনাহত হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আবার ছোটভাই মন্টু কারাখানার দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পড়ে থাকে। সব পরিস্থিতিকে একা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে নীতা।

ধীরে ধীরে নীতার শরীর ভেঙে পড়ে। যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়েও সে কাউকে জানায় না, স্বেচ্ছা নির্বাসনে পড়ে থাকে বাড়ির এক কোণে। সংসারে এক সময় স্বাচ্ছন্দ্য ফেরে। বড় ভাই শংকর পুরোদস্তুর ক্লাসিক্যাল গায়ক হয়ে ফিরে আসে। অসুস্থ নীতাকে সে ভর্তি করে শিলং পাহাড়ের এক হাসপাতালে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নীতা জানায় বেঁচে থাকার আকুতি। মূলত মধ্যবিত্ত পরিবারটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নীতার নিঃস্বার্থ সংগ্রাম এবং তার করুণ পরিণতি ঋত্বিক ঘটক অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই চলচ্চিত্রে।
নীতাদের এই মধ্যবিত্ত পরিবারটি দেশভাগের যন্ত্রণা বহন করা উদ্বাস্তু শত শত পরিবারের একটির প্রতিনিধি। নতুন দেশ এবং পরিবেশ তাদেরকে এক জটিল এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে। প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার লড়াইয়ের আবেগঘন এই গল্পটি গভীর মমতায় উপস্থাপন করেছেন চলচ্চিত্রকার। ফলশ্রুতিতে এক নিবিষ্ট চিত্তে দেখার সময় এর চরিত্রগুলো বড় আপন হয়ে ওঠে। প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টিতে এবং তাদের মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে চলচ্চিত্রকার যে যত্নের পরিচয় দিয়েছেন তার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় ফ্রেমে ফ্রেমে।

‘মেঘে ঢাকা তারা’র প্রধান চরিত্র নীতা অচেনা কোনো মানুষ নয়, বরং চলচ্চিত্রটি দেখার সময় আমাদের চারপাশের নীতাদের আমরা নতুন করে আবিষ্কার করি। নীতা আমাদের পরিবারের সেই চরিত্রটি, যার কাছে নিজের থেকে অন্যরা মুখ্য হয়ে ওঠে। টিউশনির টাকা পেয়ে নিজের ছেঁড়া চটিজোড়া বদলে সে নতুন জুতা কেনে না, অথচ বোন গীতাকে নতুন শাড়ি, ছোটভাই মন্টুকে ফুটবল খেলার জন্য বুট, দাদা শংকরকে একটা পাঞ্জাবির কাপড় কিনে দিয়ে সে নির্দ্বিধায় সব টাকা শেষ করে ফেলে।
নিজেকে উজাড় করে দিয়ে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায় অন্যের স্বপ্নগুলো। নীতার দাদা শংকরকে নিয়ে অন্যরা যখন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত এবং অসন্তুষ্ট, তখন দাদার গায়ক হওয়ার স্বপ্নটিকে সে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। সরাসরি চাকরিতে না ঢুকে পিএইচডি করার সুযোগ সন্ধান করতে উৎসাহিত করেছে প্রেমিক সনৎ-কে। কাজেই নীতার মাঝে আমরা খুঁজে পাই আমাদের চারপাশের নিঃস্বার্থ মানুষগুলোকে যারা ভালবাসতে জানে প্রাণভরে। এভাবেই ধীরে ধীরে নীতা চরিত্রটি আমাদের আপন হয়ে উঠতে থাকে।
দারিদ্র্যের এই কঠিন রূপটির উপস্থাপনায়ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এই চলচ্চিত্রে। হাস্যরস এবং ভাই-বোনের খুনসুঁটির সাথে সাথে মধ্যবিত্ত পরিবারের মাধুর্যের দিকটি এখানে যেমনভাবে এসেছে, তেমনিভাবে অভাবের কঠিন রূপটিও আমরা দেখি। এই চলচ্চিত্রে নীতা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, শংকর চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং সনতের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নিরঞ্জন রায়।

নীতার স্কুলশিক্ষক বাবাকে আমরা আবিষ্কার করি একটি খেয়ালি চরিত্র রূপে। তিনি আপন মনে কখনও কখনও উচ্চারণ করেন শেলী অথবা ইয়েটসের কবিতা। দারিদ্র্য তার ছেলেমানুষের মতো চঞ্চল মনটিকে খুব বেশি রুখতে পারেনি। কিন্তু দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত একটি রুক্ষ চরিত্ররূপে আমরা দেখতে পাই নীতার মাকে। দারিদ্র্য কীভাবে আপন স্বার্থকে নগ্ন করে তোলে, তা ফুটে ওঠে তার চরিত্রে। এমনকি নীতার বিয়ে হয়ে গেলে সংসার কে দেখবে, এই ভয়ে নীতার ভবিষ্যৎকে অগ্রাহ্য করে তার বিয়ে দিতেও তাকে অস্বীকার করতে দেখা যায়।
এছাড়া নীতার দুই ছোট ভাই-বোন মন্টু এবং গীতার মাঝে প্রকট হয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা। নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যতই তাদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। নীতার প্রেমিক সনতকেও গ্রাস করেছে এই স্বার্থান্ধতা। সনতই নীতাকে দেখতে পেয়েছিল একটি মেঘে ঢাকা তারা রূপে, চারপাশের নানা সমস্যার মেঘে যে তারাটি ঢাকা পড়েছে। অথচ পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সনতকে নীতা যখন বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলে, তখন সে নির্লজ্জের মতো বিয়ে করে নীতার ছোট বোন গীতাকে।

আঞ্চলিক ভাষাকে পরিবেশ অনুসারে ব্যবহারের নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় এই চলচ্চিত্রে। চিত্রনাট্যের প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়ে পরিচালকের মনোযোগ এর গল্পটিকে করে তুলেছে আরও বিশ্বাসযোগ্য। গীতার সাথে সনতের বিয়ের আগের মুহূর্তটি খুবই মর্মস্পর্শী। সবাই এই বিয়ের পেছনের নির্মমতা অনুভব করেও নিস্পৃহ থাকার অভিনয় করতে থাকে। কেবল নীতার শয্যাশয়ী বাবা আকুল হয়ে বলে ওঠে,
“সেকালে মাইনষে গঙ্গা যাত্রীর গলায় ঝুলাইয়া দিতো মাইয়া, তারা ছিল ‘বর্বর’। আর একালে আমরা শিক্ষিত, সিভিলাইজড। তাই লিখাপড়া শিখাইয়া মাইয়ারে নিংড়াইয়া, ডইল্যা, পিষ্যা, মুইছা ফেলি তার ভবিষ্যৎ। ডিফারেন্সটা এই।”
এই ধূলি ধূসরিত পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্রতাকে পায়ে দলে মাঝে মাঝে কেউ নিজেকে নিয়ে যায় অন্য স্তরে, ভালবাসার কোমল আবরণে সে ঢেকে দিতে চায় পুরো পৃথিবীকে। এই চলচ্চিত্রের নীতা তাদেরই একজন। বাবার এই করুণ কণ্ঠ শুনে নীতা নিজের চোখের জল এবং লজ্জাকে লুকানোর জন্য সজোরে বলে ওঠে,
“ও মা! বেলা যে পইড়া আইলো। তোমার চা খাওনের সময় হইছে। চা আইনা দেই। কে কে চা খাবে?”
এমন টুকরো টুকরো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নীতার সেই অপার্থিব রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
এ চলচ্চিত্রে সঙ্গীত ব্যবহারের মুন্সিয়ানার কথা আলাদাভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীতের পশাপাশি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীতকেও চমৎকারভাবে এর সঙ্গীত পরিচালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র অন্তর্ভুক্ত করেছেন এই চলচ্চিত্রে। পাশাপাশি চলচ্চিত্রের প্রবাহের সাথে মিলিয়ে আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টিতে আবহ সঙ্গীতের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ এবং আবহসংগীতের এই সুনিপুণ সমাবেশই চলচ্চিত্রটিকে করে তুলেছে অনন্য।

এই চলচ্চিত্রের শেষের অংশটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। শিলং পাহাড়ের এক বক্ষব্যধি হাসপাতালে অসুস্থ নীতাকে দেখতে আসে তার দাদা। আনন্দমাখা কণ্ঠে জানায়, তাদের ঘরটি এখন দো’তলা হয়েছে। গীতার সদ্যোজাত শিশুটি কিভাবে নানা দুষ্টুমিতে মাতিয়ে রাখছে তাদের বাড়িটিকে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সেই আনন্দময় পরিবেশ কল্পনা করে বাঁচতে বড়ো শখ হয় নীতার। কান্নাভরা গলায় তার দাদাকে সে চিৎকার করে বলে,
“দাদা, আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমি যে বাঁচতে বড় ভালবাসি। দাদা, আমি বাঁচব। দাদা, আমি বাঁচব।”
নীতার বেঁচে থাকার এই সকরুণ আকুতি ধ্বনিত হতে থাকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। এই মুহূর্তটিকে ঋত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,
“মানুষের অবক্ষয় আমাকে আকর্ষণ করে। তার কারণ এর মধ্য দিয়ে আমি দেখি জীবনের গতিকে, স্বাস্থ্যকে। আমি বিশ্বাস করি জীবনের প্রবহমানতায়। আমার ছবির চরিত্ররা চিৎকার করে বলে আমাকে বাঁচতে দাও। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে বাঁচতে চায়- এ তো মৃত্যু নয়, জীবনেরই জয়ঘোষণা।”
অর্থাৎ নীতার এই বেঁচে থাকার আকুতির মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার গাইতে চেয়েছেন জীবনেরই জয়গান। নীতাদের যে কোনো মৃত্যু নেই, তা স্পষ্ট হয় ঋত্বিকের সৃষ্ট বৃত্তে। চলচ্চিত্রের শুরুতে পথিমধ্যে নীতার চটিজোড়া ছিঁড়ে গেলে সে বাড়ি ফিরেছিল জুতাজোড়া হাতে নিয়ে। চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যেও পাথরের রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে আরেকটি মেয়ের চটিজোড়া ছিঁড়ে যায়। চলচ্চিত্রের শুরুতে এবং শেষে এই চটি ছেঁড়ার বৃত্তের মাধ্যমে ঋত্বিক আমাদেরকে দেখান, নীতারা কখনো হারিয়ে যায় না, তারা যুগে যুগে আমাদের মাঝেই বেঁচে থাকে।

সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালি’র পর বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চর্চিত চলচ্চিত্র ‘মেঘে ঢাকা তারা’। মধ্যবিত্তের জীবনের এই সুনিপুণ গল্পটির কোনো মৃত্যু নেই, তাই এতটা বছর পরেও চলচ্চিত্রটির আবেদন পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ন রয়েছে।
অনলাইনে কিনুন- মেঘে ঢাকা তারা