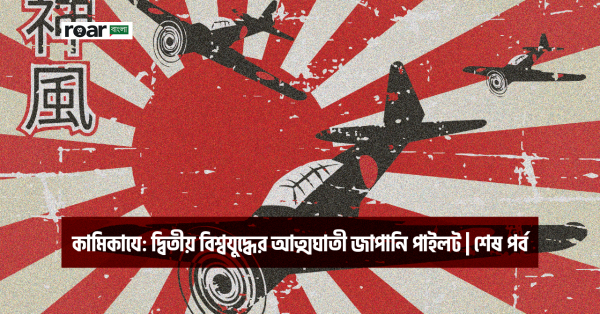আগের পর্বে বিশ্বঅর্থনীতি ও বিশ্বসংস্কৃতিতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষ অবস্থান, অতীতের কোরিয়া উপদ্বীপের যুদ্ধের ফলাফল ও দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ভগ্নদশা, সামরিক শাসক পার্ক চুং-হি’র দূরদর্শী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বে বিশ্ব-অর্থনীতিতে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্থান, দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় আয় বৃদ্ধির কারণ এবং পার্ক চুং-হির সামরিক শাসনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
১৯৭০ সালের আগপর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো বহির্বাণিজ্যের প্রতি খুব বেশি নজর দেয়নি। কারণ গতানুগতিক কাপড়, জুতা ইত্যাদি রপ্তানির পেছনেই সমস্ত পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলো। কিন্তু এই পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকায় খুব বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বাইরের দেশে ইলেক্ট্রনিক পণ্য রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয় এবং সফলতা লাভ করে। স্যামসাং টেলিভিশন, রেডিও ও ওয়াশিং মেশিন রপ্তানি শুরু করে। ১৯৭৫ সালে হুন্দাই কোম্পানি তাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গাড়ি নির্মাণ করে। প্রাথমিকভাবে রপ্তানির পর দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে এই পণ্যগুলোর বিশাল চাহিদা তৈরি হয়েছে। ফলে গতানুগতিক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছেড়ে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের দিকে বেশি বিনিয়োগ করতে শুরু করে এই কোম্পানিগুলো।
ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য তৈরিতে সেমিকন্ডাক্টর এক অপরিহার্য উপাদান। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তিনির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিকভাবে জাপান এবং আমেরিকার সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এটি আমদানি করছিল। কিন্তু এর কারণে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছিল, যা দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য ভালো ব্যাপার ছিল না। এজন্য একসময় স্যামসাং ও অন্যান্য প্রযুক্তিনির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা নিজেরাই সেমিকন্ডাক্টর নির্মাণ শিল্প গড়ে তুলবে। এরই অংশ হিসেবে তারা জাপানি সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ‘শার্প’ এবং মার্কিন সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ‘মাইক্রন’ এর দ্বারস্থ হয়। ছয় মাস পর স্যামসাং নিজস্ব গবেষকদের মাধ্যমে সেমিকন্ডাক্টরের সাহায্যে ৬৪ কিলোবাইট র্যাম চিপ তৈরি করে। দক্ষিণ কোরিয়ার ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানির ইতিহাসে এটি ছিল যুগান্তকারী এক ঘটনা। এর ফলে দেশটির রপ্তানি বাণিজ্য নতুন মাত্রা লাভ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে তৃতীয় দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া এই কৃতিত্ব অর্জন করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার শাসক পার্ক চুং-হির আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল জাপানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। জাপানের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার ১৯৬৫ সালে নতুন চুক্তি হয়, চুক্তির ফলে দেশটি জাপানের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে ৩০০ মিলিয়ন ডলার লাভ করে। এছাড়া ঋণ হিসেবে জাপান আরও ৫০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে দক্ষিণ কোরিয়াকে। এই বিশাল অংকের অর্থ দেশটির অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। এছাড়া আমেরিকার অনুরোধে দক্ষিণ কোরিয়া ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে সামরিক সহায়তা, অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের বেতন এবং অর্থনৈতিক সহায়তার অংশ হিসেবে আমেরিকার কাছ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া পাঁচ বিলিয়ন ডলার লাভ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দুই বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ যুদ্ধরত দক্ষিণ কোরিয়ান সেনারা দেশে প্রেরণ করে, যেটি দেশটির জাতীয় আয় বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দশ বছরে ভিয়েতনামের রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সেনাদের প্রেরিত অর্থের দ্বারা দক্ষিণ কোরিয়ার মোট জাতীয় আয় প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

শুধু যে ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদের পাঠানো অর্থ থেকেই দক্ষিণ কোরিয়া লাভবান হচ্ছিল, বিষয়টা সেরকম নয় মোটেও। জনশক্তি রপ্তানির দিকেও পার্ক চুং-হি নজর দিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে পূর্ব জার্মানির সাথে পার্ক চুং-হি এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যে চুক্তিতে জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ে বিধান রাখা হয়েছিল। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অসংখ্য নারী ও পুরুষ পূর্ব জার্মানিতে গমন করেন। নারীরা প্রধানত নার্স হিসেবে গিয়েছিলেন, পুরুষরা গিয়েছিলেন খনিশ্রমিক হিসেবে। ১৯৭৫ সালের দিকে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো তেল রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে নিজ দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা রাস্তা, কারখানা, বন্দর ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বিশাল অংকের অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করে। এই সুযোগ লুফে নিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। দেশটির রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো মধ্যপ্রাচ্যে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অভিজাত সমাজে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তিনির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর তৈরি পণ্যগুলোর বিশাল চাহিদা তৈরি হয়েছিল।
পার্ক চুং-হির শাসনামলের অন্ধকার দিক সম্পর্কেও জানা জরুরি। তিনি ছিলেন একজন কর্তৃত্ববাদী শাসক, যিনি সবসময় চাইতেন যেভাবেই হোক, ক্ষমতা যেন দীর্ঘায়িত করা যায়। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হওয়া যেকোনো সমালোচনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। তার সময়ে যারা তার সমালোচনা করত, তাদেরকে তিনি ‘উত্তর কোরিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল’ এবং ‘ষড়যন্ত্রকারী গোয়েন্দা’ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তার সরকারি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ত্রাস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। মূলত যারাই সেসময়ে পার্ক চুং-হির ন্যূনতম সমালোচনা করেছেন, তারাই তার রোষানলে প্রাণ হারিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সহিংসতায় প্রাণ হারানো মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। এদের অনেকে বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। পার্ক চুং-হি একসময় এত বেশি কর্তৃত্ববাদী হয়ে পড়বেন যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে– এই ভয় থেকে তার গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা তাকে হত্যা করেন।

image source:hamptonthink.org
দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রবল। ছোট থেকেই তাদেরকে শেখানো হয়– ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয়, দেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সবসময়। পার্ক চুং-হির সময়ে দেশটির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং জাতীয় পতাকার মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য শপথ পাঠ করা বাধ্যতামূলক ছিল। ১৯৮৭ সালে দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর এসব ঐচ্ছিক করে দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও দক্ষিণ কোরিয়ার তরুণেরা নিয়মিত একত্রিত হয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে, শপথনামা পাঠ করত। ১৯৯০ সালের দিকে যখন এশিয়ার উদীয়মান দেশগুলোর অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয়, তখন ঋণের বেড়াজাল থেকে দেশকে বাঁচাতে দক্ষিণ কোরিয়ার অসংখ্য নাগরিক তাদের কাছে থাকা সোনা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন। এই দুটি ঘটনা থেকে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পর্কে একটু ধারণা পাওয়া সম্ভব। এছাড়া দেশটির কর্পোরেট জগতেও সবসময় বোঝানো হয় যে ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আজকের উন্নত দক্ষিণ কোরিয়ার পেছনে দেশটির জনগণের এই মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পার্ক চুং-হি-কে বলা হয় দক্ষিণ কোরিয়ার ‘অর্থনৈতিক উত্থানের পিতা’। রাজনৈতিকভাবে তিনি কর্তৃত্ববাদী হলেও তার দেশ দক্ষিণ কোরিয়া যেন অর্থনৈতিকভাবে টেকসই সাফল্য লাভ করতে পারে, সেজন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া দরকার, তার সব তিনি নিয়েছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়া আজকে যে অবস্থানে আছে, এর পেছনে তার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যে দেশ তিন বছরের পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল, সেই দেশকে দুই দশকের মধ্যেই বিশ্ব-অর্থনীতিতে শক্ত অবস্থান এনে দেয়া মোটেও সহজ কাজ ছিল না। দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকেরা ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন, দেশের স্বার্থকে সামনে রেখে এগিয়ে গিয়েছেন সবসময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে দেশগুলো অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্দান্ত সাফল্য দেখিয়েছে, সেসবের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার নাম উচ্চারিত হবে নিঃসন্দেহে।