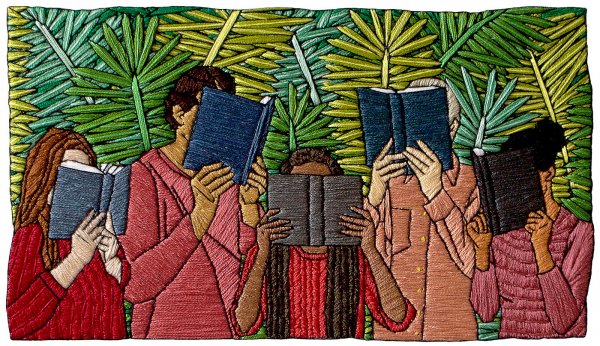বন্ধু ভাড়া নিন! শুনলে অদ্ভুত শোনালেও গোটা বিষয়টি আসলেই কৌতূহল উদ্দীপক। সিনেমার সময় ৯০ দশকে। ইন্টারনেটের গণজোয়ার তখনো আসেনি। এখনকার মতো; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপরিচিত কারো সাথে হঠাৎ করে কথা, তারপর প্রেমে পড়া, হুট করে একদিন দেখা- এসবের সুযোগ তখন ভাবনাতীত। অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষদের জন্য তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আজকাল আশীর্বাদের মতো কাজ করছে। কিন্তু তখনকার অন্তর্মুখী মানুষগুলো বন্ধু বানানোর জন্য, প্রেমিক বা প্রেমিকা জোটানোর জন্য কী করত? সিনেমার সাথে সাযুজ্য রেখে বললে প্রশ্নটা হয়, কোথায় যেত?
উত্তরে, পণ্যের প্রচারণার স্টাইলে বলতে হয়, অমুক ভিডিও স্টোরে যেত। এখানে একাকিত্ব আর নির্জীবতায় ভোগা নানান অন্তর্মুখী নারী-পুরুষ আসে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অতি স্বল্প সময়ে নিজেদের পরিচয় এবং নিজেদের নিয়ে একটুখানি ধারণা দেয়। ভিডিও স্টোরটি তারপর সেই ভিডিও ক্যাসেট পাঠায় তাদের অন্যান্য কাস্টমার তথা ব্যবহারকারীর কাছে। বলা যায়, এখনকার টিন্ডারের ভি.এইচ.এস ভার্সন এই ভিডিও স্টোর। ওমন কিছু যদি ৯০-এ সত্যিকার অর্থেই থেকে থাকত, তাহলে হয়তো সেখান থেকেই আজকের টিন্ডারের ধারণা এসেছে।
তো এই ভিডিও স্টোরে এসেছে সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রটি। দৈহিক গঠনে খুবই শক্তপোক্ত একজন মানুষ। কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয়, ভঙ্গুর প্রকৃতির এবং খুবই আবেগী একজন পুরুষ। এবং বাস্তবে তেমনটাই। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তার। মায়ের ডিমেনশিয়া আছে। মায়ের দেখাশোনাতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় এই ডেভিডকে। ফুসরত মেলার সুযোগই নেই। মেলে যেটুকু, সেটুকু অলস ভঙ্গিতে সোফায় বসে মদের গ্লাস হাতে টিভি দেখতে দেখতে অনর্থক কাটে।
কিন্তু এই একঘেয়ে জীবন আর কত? নিজেরও তো একজন সঙ্গী দরকার। হতে পারে স্বার্থপর চিন্তাভাবনা। কিন্তু সেটিকে এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই। আর সে উদ্দেশ্যেই ভিডিও স্টোরে গিয়ে নিজের সংক্ষিপ্ত বায়ো রেকর্ড করল ডেভিড, কেউ যদি সাড়া দেয়- এই আশায়। কিন্তু সাড়া এল না বেশ কয়েকদিন কাটার পরও। তাই সে ফের গেল ওই স্টোরে। না, তার উদ্দেশ্যে কোনো বার্তা নেই।
তবে অদ্ভুত একটা ভিডিও টেপ ডেভিডের হাতে পড়ল। নাম লেখা, ‘রেন্ট-আ-প্যাল’। নিঃসঙ্গ ডেভিড অগত্যা সেটি হাতে নিয়ে বাড়িতে ফিরল। রেন্ট-আ-প্যাল টেপটি মূলত একটা রেকর্ড করা শো। একজন উপস্থাপক আছে, নাম অ্যান্ডি। একাকিত্বে ভোগা লোকেদের আজীবনের বন্ধু হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয় সে। গোটা রেকর্ডেড শো’তে নানান প্রশ্ন করে অ্যান্ডি। আর প্রতিটি প্রশ্নের পর বিরতিটা এমনভাবে রাখে, যাতে মনে হয়, উত্তরটা সত্যি সত্যিই যেন শুনতে পাচ্ছে সে। আর বিষয়গুলো সে এমনভাবে উত্থাপন করে, যাতে করে রেকর্ডেড শো হলেও একটা ধূসর রেখা আর দ্বন্দ্বে ঘোরাঘুরি করে গোটা ব্যাপারটা। ধীরে ধীরে অ্যান্ডিকে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।
আসলে সেই পরিবর্তনটা ঘটছে ডেভিডের মনস্তত্ত্বে। একাকিত্ব থেকে বাঁচতেই হোক আর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই হোক, একটা রেকর্ডেড শো’র এই উপস্থাপকের সাথে সত্যিই একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে ডেভিড। এবং দেখা যায়, সময় গড়াতেই অ্যান্ডি টিভি পর্দায় থেকেও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে ডেভিডের ব্যক্তিজীবনে। শুধু তা-ই নয়, অ্যান্ডির এই শোটির প্রতি সে এতই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে, কিংবা অ্যান্ডি তাকে এতই মোহাবিষ্ট করে ফেলে যে, বাস্তব আর সাজানো বাস্তবের পার্থক্য ভুলে ভয়াবহ এক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলতে থাকে সে।

Image Source: Pretty People Pictures
‘রেন্ট-আ-প্যাল’, মূলত একটি চরিত্রনির্ভর ড্রামা সিনেমা, সাইকোলজিক্যাল ড্রামা। ক্ষেত্রবিশেষে থ্রিলার। হররটা এসেছে এর নিগূঢ় আবহে। ইউনিক প্রিমাইজ এই সিনেমার বড় শক্তি। এবং সেই প্রিমাইজকে পুঁজি করে জনরা অলংকারের যথোপযুক্ত ব্যবহারে একটি বুদ্ধিদীপ্ত সিনেমা হয়ে উঠেছে ‘রেন্ট-আ-প্যাল’। এ সিনেমা তার জগত তৈরি করতে কোনোরকম তাড়াহুড়ো করেনি, সময় নিয়েছে পর্যাপ্ত। সিনেমার প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে ডেভিডের সংকীর্ণ এবং বদ্ধ জগতের সৃষ্টিতে। সে জগত সম্পর্কে দর্শককে ধারণা দিয়েছে। অসুস্থ মায়ের প্রতি তার আনুগত্য দেখিয়েছে, আবার তার মাঝে যে একটা ‘টক্সিক’ অনুভূতি প্রোথিত আছে, সেটিও উপস্থাপন করেছে।
আর দ্বিতীয় অঙ্ক এগিয়েছে টিভি পর্দায় অ্যান্ডির সাথে ডেভিডের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে। ধীরে ধীরে কীভাবে একটা রেকর্ডেড শো’র উপস্থাপকের সাথে ডেভিড একাত্ম হয়ে উঠছে, তার গোটা প্রক্রিয়াটাই এ সময়ে উঠে এসেছে। ডেভিড মানসিকভাবে একটা টিভি পর্দার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে, পর্দায় ফুটে ওঠা মানুষটাকে তার বাস্তব জীবনের বন্ধু ভাবছে; এই দৃশ্যগুলো সিনেমার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ। সেইসাথে একটা অস্বস্তি আর চাপা ভয়ও কাজ করে। তৃতীয় অঙ্ক পুরোপুরিই আবর্তিত হয়েছে, আশপাশের জগতের খেয়াল হারিয়ে ডেভিডের বাতুলতার চরম সীমায় পৌঁছানো নিয়ে।

Image Source: Pretty People Pictures
সিনেমার প্রেক্ষাপট ৯০-এ হলেও, সুকৌশলে বর্তমানে যুগের ভয়াবহ ইন্টারনেট আসক্তির দিকটিকেই রূপকার্থে তুলে ধরছে এই সিনেমা। সেইসাথে একাকিত্ব, আচ্ছন্নতা, কড়া পৌরুষবোধের বিষয়গুলোকেও উপস্থাপন করেছে। তবে বিষয়াদিতে যে প্রগাঢ়তা ছিল, তার সবটুকু এ সিনেমা ব্যবহার করতে পারেনি। যত্ন নিয়ে লেখা প্রথম দুই অঙ্কের পর তৃতীয় অঙ্কে চিত্রনাট্যকার জন স্টিভেনসন সেই সংহতি ধরে রাখতে পারেননি। নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে, নিজের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে ডেভিডের যে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা, সেটাকে তৃতীয় অঙ্কে গড়পড়তা জনরা অলঙ্কারে বেঁধে ফেলেছেন তিনি। গোর আর ভায়োলেন্সই সেখানে মূল উপজীব্য।
চিত্রনাট্যে যে শক্তিশালী একটা চরিত্র তিনি দাঁড় করিয়েছেন, সেটা নিয়ে শেষ অব্দি কোথায় যাবেন, তা যেন বুঝতে পারছিলেন না। সিনেমার গোটা ন্যারেটিভের মাঝে একটা বিচ্যুতি এনে দিয়েছে এই অংশ। এছাড়া, কে এই অ্যান্ডি? কেনই বা এই শো তৈরি করল সে? এসব প্রশ্ন দর্শকের মনে উঁকি দেয়, যার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে সেটাকে খণ্ডন করা যায় এই বলে, গোটা সিনেমাই ডেভিডের দৃষ্টিকোণ ধরে বর্ণিত। তার বদ্ধ জগত অ্যান্ডির অস্তিত্বের গভীরে অনুসন্ধান চালায়নি, তাই সিনেমাও চালায়নি। অ্যান্ডিকে টিভি পর্দায় রেখে দর্শকের মাঝে একটা আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের ভাব জাগানো এবং ওই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে একটা অস্পষ্টতায় ডুবিয়ে রাখাটাই হয়তো সিনেমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।
অ্যান্ডি চরিত্রটি যেমন অদ্ভুত আর ভয় জাগানিয়া, এ চরিত্রে ঠিক তেমন অভিনয়ই উপহার দিয়েছেন উইল ওয়েটন। সারাটা সময় টিভি পর্দার ভেতরে আটকে থেকে ডেভিডের মনস্তত্ত্বে তো বৈ, গোটা সিনেমায়ও প্রভাব বিস্তার করা কম কথা নয়। তার হাসি হাসি মুখ, বন্ধুত্বের আহ্বান করা চোখের তারায় হঠাৎ করে ক্ষণিকের পরিবর্তন, ধন্দে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে চরম অস্বস্তিতে। ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসে উঠে ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত রেখে চোখ সরু করে মেলা ওই দৃষ্টি ভয় জাগাতে পারে অনায়াসে।
ওদিকে ডেভিড চরিত্রে ব্রায়ান ফলকিন্সের অভিনয় তার প্রতি সহমর্মিতা জাগাতে বাধ্য করে। তার ভঙ্গুরতা শেষে যখন উন্মত্ততায় পৌঁছে, তখনো তার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক প্রবল আকারে ঘটে না। কারণ এর আগে যে নিঃসঙ্গ ডেভিডকে দর্শক প্রত্যক্ষ করেছে। দর্শক দেখেছে, প্রথম ডেটের পর কীভাবে বাচ্চাদের মতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল ডেভিড। তার প্রেমিকাসুলভ লিসা চরিত্রটির গঠনবিন্যাস নিয়ে আপত্তির জায়গা থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে ডেভিডের দুনিয়ায় তার স্থান কতটুকু, যেহেতু গল্প ডেভিডের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত। ডেভিডের টক্সিক দিকটার প্রকাশেই মা আর প্রেমিকার চরিত্রগুলো কাজ করেছে এবং সেগুলো তাই ওভাবেই স্থান পেয়েছে। লিসা চরিত্রটিতে স্বল্প সময়ে কমনীয় অভিনয় উপহার দিয়েছেন অ্যামি রাৎলেজ।

Image Source: Pretty People Pictures
চিত্রনাট্যের পাশাপাশি পরিচালনা আর সম্পাদনার কাজটাও জন স্টিভেনসন করেছেন। এবং দুটো জায়গাতেই কুশলী কাজ করেছেন তিনি। ডেভিড আর টিভির পর্দায় থাকা অ্যান্ডির আলাপচারিতার অংশগুলোতে বারবার কাট করে পরবর্তী সময়ে এমনভাবে জোড়া লাগিয়েছেন; মনে হচ্ছিল, আলাপটা মুখোমুখি বসে হচ্ছে। খুবই সূক্ষ্ম তার সম্পাদনা শৈলী। ওদিকে প্রোডাকশন ডিজাইনে ডেভিডের ছোট্ট দুনিয়ায় সময়ের ধারণাটা ঠিকঠাক রাখতে যত যা বিবরণ লাগে, সবকিছুই যথাযথভাবে এনেছেন। ৯০ দশকের ভাবটা সে কারণে পুরোপুরিই পাওয়া যায়। ডেভিডের সংকীর্ণ দুনিয়ার ভিজ্যুয়ালাইজেশন নিখুঁত রূপেই হয়েছে। ওয়াইড শটে তার ছোট্ট জগত আর ক্লোজে তার জংধরা অস্তিত্ব ক্লস্ট্রোফোবিক অনুভূতি জাগায়। নীলের আভায় যেন ঠিকরে উঠেছে তার বিচ্ছিন্ন জগত।
কিছু সংকীর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ‘রেন্ট-আ-প্যাল’ বুদ্ধিদীপ্ত একটি কাজ হয়েছে। অভিনব ধারণাটিকে বিফলে যেতে দেয়নি। হররের আবহে চরিত্রনির্ভর ড্রামা সিনেমা হয়েছে বলে, দেখার অভিজ্ঞতায় ভাটা পড়েনি আবার। ওভাবেই দেখা দরকার সিনেমাটিকে।