.jpg?w=1200)
দাদা- এই শব্দটি বর্তমান সমাজে যেরকম উদ্ধত ভঙ্গির পরিচায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, শব্দটির এমন ব্যবহার কিন্তু আশির দশকের বাঙালি সমাজে ছিল না। তখন ‘দাদা’ বলতে এক স্নেহ-শাসন মিশ্রিত, পরোপকারী, সদা প্রাণোচ্ছ্বল তরুণকে বোঝাত। বিশেষত, পাড়ার দাদাদের ক্ষেত্রে এই বিশেষণগুলো দারুণভাবে প্রযোজ্য ছিল। রাতদুপুরে অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই হোক বা মড়া পোড়ানো, কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের বরপণ জোগাড় করে দেওয়াই হোক বা এ পাড়ায় প্রেম করতে আসা বেপাড়ার প্রেমিককে অল্প ভয় দেখানো, এসব ‘দাদাগিরি’ পরম্পরায় করে আসতেন তারা।
এসব দাদাদের চাকরি-বাকরি তেমন ছিল না বললেই চলে, বা থাকলেও সে নাম-কা-ওয়াস্তে ছোটখাট কোনো কাজ। মূলত মানুষের কাজকেই জীবনের পরম ধর্ম বলে মেনে নিতেন তারা। বলা বাহুল্য, পাড়ার মানুষদের কাছে এই ভরসাযোগ্য দাদাদের গ্রহণযোগ্যতা বরাবরই ছিল উচ্চমানের।
সময় পাল্টেছে, পাড়া-সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটেছে অজান্তেই। নিখাদ পরোপকার করে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার ‘অনগ্রসর’ মনোবৃত্তি অতিবড় বোকাও আজকে ভাবে না। চূড়ান্ত কেরিয়ারিস্ট (careerist) মনোভাবের আমদানি যেমন ঘটেছে, তেমনই বেকার, অকর্মণ্যদের আশ্রয়স্থল হিসেবে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দলের ছাদ। সেসব দাদারা কিন্তু সেই অর্থে রাজনৈতিক দাপটের ধার ধারতেন না। তারা দাদাগিরিটা করতেন একটা অভিভাবকসুলভ নৈতিকতার দিক থেকেই। তাই আজ তাদের আক্ষেপ করে বলতে হয়-
“সে কালে উঠতি বয়সের ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই পরোপকারের নেশা ছিল। বলতে পার ওটুকুই সে যুগের দাদাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরে রাজনীতি গোটা সমাজটাকেই গ্রাস করে নিল। রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব নেই, এমন মানুষের হাত থেকে সামাজিক ক্ষমতা হারিয়ে গেল। ইদানিং তো উঠতে বসতেও রাজনীতি। সবার আগে জানাতে হবে, তুমি কোন দলে? দল যদি দশে মিলি কাজের সত্যিকারের দৃষ্টান্ত হত, তা হলে বলবার আর কিছুই থাকে না।”
সম্প্রতি লেখক অর্ণব দত্ত ‘পাড়ার দাদা, একটি লুপ্তপ্রায় প্রজাতি’ শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন-
“সে কালের পাড়ার দাদারা হয়তো এই ধরাধামে সশরীরে বসবাস করবেন বড়জোর আরও কয়েক বছর। এরপর চিরকালের মতো তাঁরাও বিদায় নেবেন ঘুমের দেশে। জীবনের উপান্তে পৌঁছনো এসব মানুষগুলোর পিছুটান বলতে এখন শুধুই ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি।”
আমরা বরং পাড়ার দাদাদের বিলুপ্তির বিয়োগান্ত অধ্যায়টিকে বাদ দিয়ে তাদের সেসব গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথাই ভাবি। এদের থেকেই বাংলা কথাসাহিত্য পেয়েছিল কালজয়ী কিছু চরিত্র, যাদের গল্প মাতিয়ে রেখেছে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম। যেমন ঘনাদা, টেনিদা বা ব্রজদা, যাদের গুলতানির কোনো বয়স হয় না। এসব দাদাদের কাহিনী নিয়ে ২০০২ কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় নির্মল বুক এজেন্সি প্রকাশনা থেকে শ্যামলকান্তি দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘১০০ দাদার ১০০ গল্প’ নামের একটি সংকলন। দুর্লভ সংকলন বলা চলে, যা কেবলমাত্র বোধহয় বাংলা সাহিত্যেই সম্ভব।
প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদাকে যদি এদের সকলের চেয়ে বয়োঃজ্যেষ্ঠ হিসাবে ধরা যায়, তবে তাকে দিয়েই শুরু করা ভালো। ঘনাদার প্রথম গল্প ‘মশা’ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালের দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী ‘আলপনা’-তে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাত্র হিসেবে ছিলেন মেধাবী, পড়াশোনা করতেন প্রচুর। সাহিত্যকীর্তি তার প্রধান কাজ হলেও তিনি বিজ্ঞানের উৎসাহী ছাত্র ছিলেন। শ্রীনিকেতনে পড়েছেন কৃষিবিজ্ঞান, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পড়েছেন ডাক্তারি। মন দিয়ে পড়তেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা। খুঁটিয়ে দেখতেন পৃথিবীর মানচিত্র, সাথে চলত ইতিহাসচর্চা। ফলে ঘনাদাকে গড়লেন এমন এক চরিত্র হিসেবে, যিনি ইতিহাসের পাশাপাশি বিজ্ঞানটাও ভালো জানেন।
মনে রাখতে হবে, তখন সদ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সামরিক আগ্রাসনের বীভৎস রূপ দু’পক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছে পৃথিবী। প্রেমেন্দ্র নিজে ছিলেন ‘ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে’র সদস্য। ঘনাদাও হয়ে উঠলেন হিংসার পৃথিবীতে মানবতার দূত। জাপানি বিজ্ঞানী নিশিমারার মশার লালাকে অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়া থেকে যার জয়যাত্রার শুরু। তারপর কখনো রুজভেল্টের অনুরোধে জার্মানদের পরমাণু বোমা বানানোর পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়া, কিংবা উন্মাদ ইহুদী বিজ্ঞানী জেকব রথস্টাইনের সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়ার ঝাঁককে নির্বংশ করে দেওয়া, আবার মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়া সবই ছিল ঘনাদার অভিযানের মধ্যে।
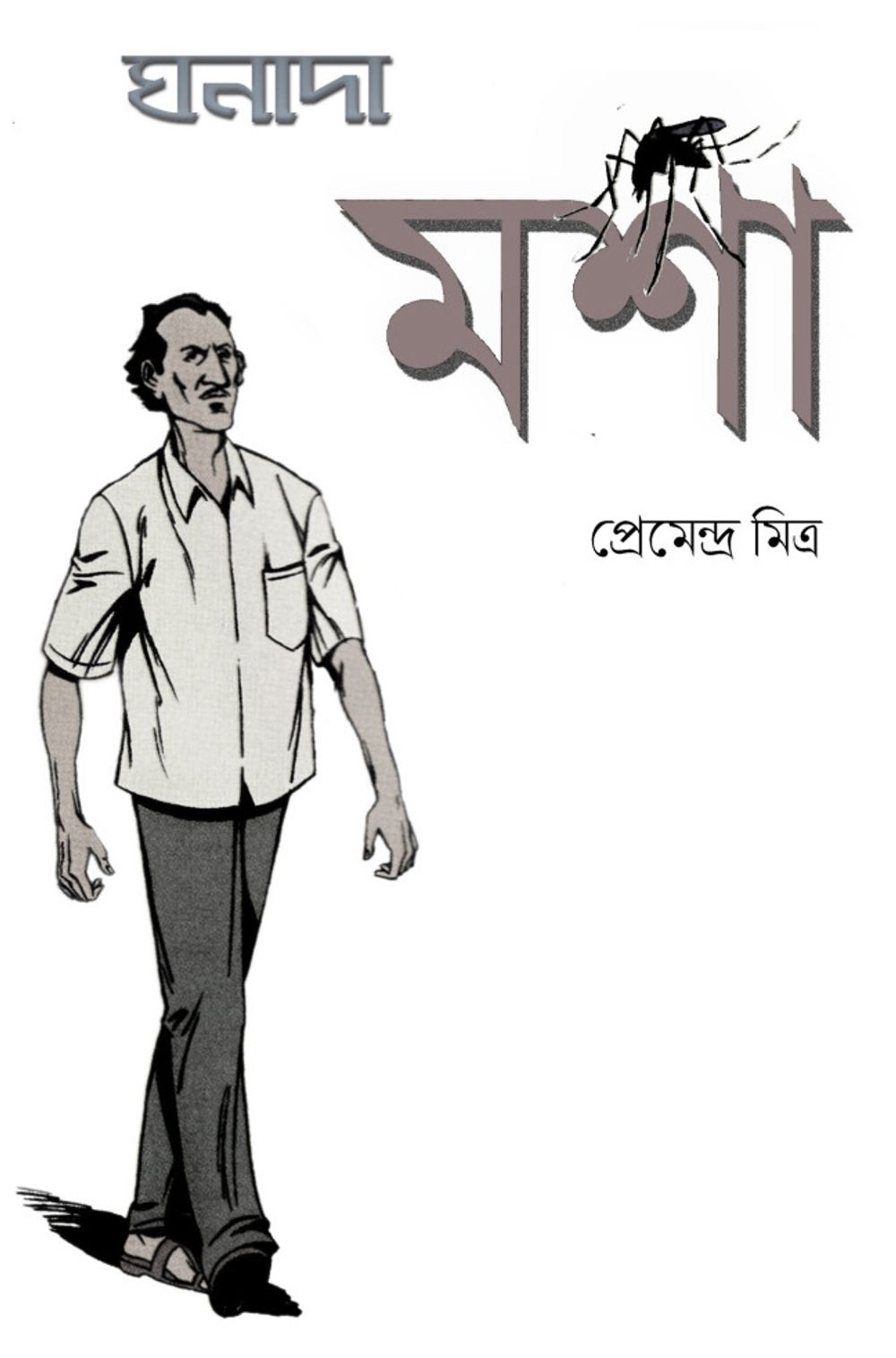
বলা বাহুল্য, এসব গল্পই আজগুবি এবং বানানো। ঘনাদার ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির ঠিকানায় সন্ধের মজলিশে তৈরি হতো এসব গল্প। গুল জেনেও হাঁ করে গিলতেন তার চার শাগরেদ শিশির, শিবু, গৌর আর সুধীর। প্রেমেন্দ্র মিত্র থাকতেন গোবিন্দ ঘোষাল লেনের মেসবাড়িতে। সেখানকার মেসের বাসিন্দা বিমল ঘোষকে দেখে তার মাথায় এসেছিল ঘনাদার ভাবনা, এমনটা বলে থাকেন অনেকেই। সামান্য জিনিস দেখেই ঘনাদার মাথায় ঘুরত গল্প। গুবরে পোকা দেখে তার মাথায় এসেছিল সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া, যে নাম কষ্মিনকালেও কোনো পতঙ্গবিদ্যার বইতে থাকার কথা নয়। কাচ দেখে বানিয়ে ফেললেন বিশেষ যন্ত্র। কাচের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে কীভাবে আফ্রিকার জঙ্গলে জংলী তাড়িয়েছিলেন, আর কীভাবে নাৎসিদেরও পিচব্লেন্ড নেওয়া প্রতিহত করেছিলেন সেসব গল্প আছে ঝুলিতে।
ঘনাদার চেহারা ছিপছিপে, অথচ তিনি নিয়মিত যোগব্যায়াম করতেন, এবং ক্যারাটে-যুযুৎসুর প্যাঁচ জানতেন বলে দাবি করেন। তবে মানুষটি খাদ্যরসিক। চপ, কাটলেট খেতে পছন্দ করতেন বেশ। আর গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে শিশিরের কাছ থেকে ধারে নিয়ে নিতেন দামী সিগারেট। যে সিগারেটের শোকে প্রতিটি গল্পের শেষেই শিশিরকে হা-হুতাশ করতে দেখা যেত। ঘনাদার আসল নাম ছিল ঘনশ্যাম দাস। তাকে আন্তর্জাতিক জগতে সকলে ডাকত মি. ডস নামে।
ঘনাদা হয়তো বনমালী নস্কর লেনের চৌহদ্দি ছেড়ে কোথাও যাননি, কিন্তু মানসভ্রমণে তার সাথে পাল্লা দেবে এমন বুকের পাটা কার? আর স্বজাতির প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা যে পুরোমাত্রায়, তা বারবারই প্রমাণ পাওয়া গেছে। ম্যানহাটান প্রজেক্টে গেলে বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার যখন তাকে বলেন, পরমাণু বোমার প্রকল্পে তিনিও সঙ্গী হোন, ঘনাদা সটান তাকে বলেন, যে ভারত চিরকাল শান্তির বাণী প্রচার করে এসেছে, তাই এমন কোনো বিধ্বংসী প্রকল্পে যুক্ত হতে তার বিবেকে বাধে। মুখেনং মারিতং জগতের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই চরিত্রকে ভালো না বেসে কি পারা যায়?

যে উচ্চমানের গুল মারার জন্য আবির্ভাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষেও সমান জনপ্রিয় হয়ে আছেন ঘনশ্যাম দাস, অনেকটা ওই একই ধাঁচের গুল শোনা গিয়েছে আরেক বাঙালি দাদার মুখ থেকেও। সেসব গুল অবশ্য লেখকের বানানো নয়, যে ভদ্রলোককে নিয়ে গল্প তার মুখে সত্যি সত্যিই সেসব গুল শোনা যেত। তার নাম ব্রজরঞ্জন রায়। আনন্দবাজার পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক তিনি জড়িয়ে ছিলেন দৈনিকটির সঙ্গে।
নিজে খেলোয়াড় ছিলেন, পরে হয়েছিলেন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহরু এমন বহু নামীদামী লোকের সাথেই যোগাযোগ ছিল তার। সেসব যোগাযোগের গল্পকেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে হাজির করতেন সহকর্মীদের কাছে। এই ব্রজরঞ্জন রায়কে নিয়ে অনুজ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ যে চরিত্রটিকে বানিয়েছিলেন, তার নাম ছিল ব্রজরাজ কারফর্মা ওরফে ব্রজদা।
‘ব্রজবুলি’ ও ‘ব্রজদার গুল্পসমগ্র’ এই দুটি বই প্রকাশিত হয়েছিল বাস্তবের নায়কের জীবদ্দশাতেই। ঘনাদাদের আড্ডা যেমন ছিল মেসবাড়ির আস্তানায়, ব্রজদা তার সব বুলি ঝাড়তেন অফিসের টেবিলে। ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক। ঘনাদার গুলে যেমন পুঁথিগত জ্ঞানের মিশেল থাকত, ব্রজদার গুল তেমন নয়, সেগুলো নিখাদ গুল্প (গুল+গল্প)। ব্রজদা সেগুলো বলতেন সহকর্মীদের আনন্দ দিতেই।
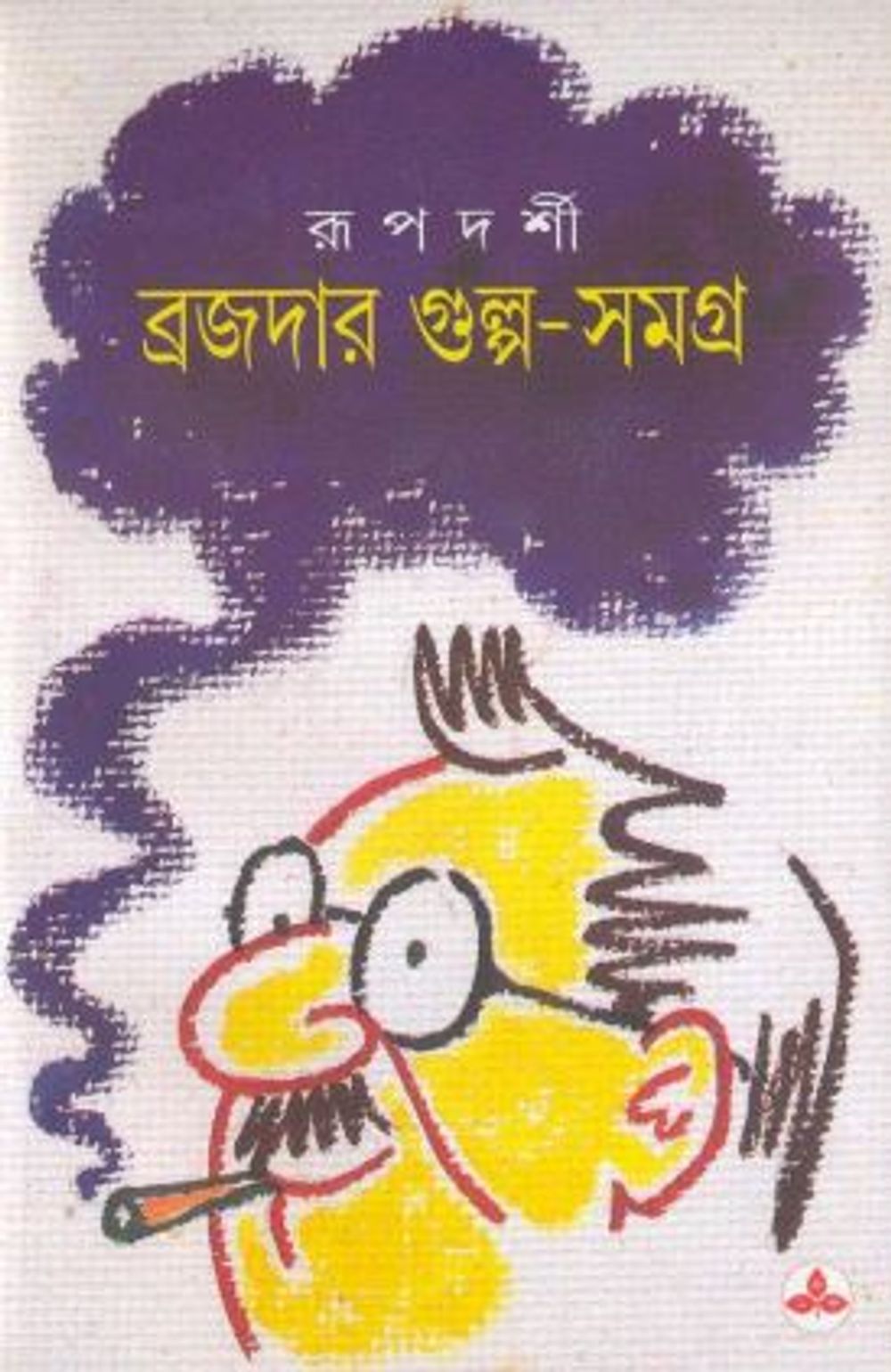
ঘনাদার মতো ব্রজদার চলাফেরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয়, তা সীমাবদ্ধ দেশীয় হোমরাচোমরা মহলেই। বিদেশে যে যাননি তা নয় (মানে তার গুল অনুযায়ী), প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সেনাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছিলেন যে প্রবাদপ্রতিম সুন্দরী মাতাহারি, সেই মাতাহারিকে ধরতে ফ্রান্সে পাড়ি দিয়েছিলেন ব্রজদা। ব্রজদার গল্পে অনেক বেশি উঠে এসেছে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ব্রিটিশ সমাজ ও বাঙালি এলিট সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক। তার অবাধ চলাফেরা ছিল ভাইসরয়ের দপ্তরেও, এমনটাই দাবি ছিল তার। তা এহেন ব্রজদাই নাকি রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থ লেখার প্রেরণা।
বড়লাটের এডিকং কর্নেল ক্লিম্যান্টকে যখন কুস্তিতে কেউ হারাতে পারছে না, তখন এই ব্রজদাই রিংয়ে নেমে তাকে ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করেন। এই গল্পটা বলতে বলতে ব্রজদা কিন্তু বাঙালির পরনিন্দার বিষয়টিকেও তীব্র সমালোচনা করেন- “যাই বলিস আর তাই বলিস, ল্যাং মারায় বাঙ্গালীর কাছে ওয়ার্ল্ডের কেউ দাঁড়াতে পারে না।” এই ক্লিম্যান্টের সাথে তারপর ব্রজদার এমনি বন্ধুত্ব হয়ে যায় যে দুজনে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে ডাল লেকে শিকারায় চড়ে বাইচ খেলা শুরু করেন, আর এই খেলতে গিয়েই হয় বিপত্তি। একটি শিকারা সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে একটি হাউসবোটে, যে বোটে নাকি স্বয়ং কবিগুরু ছিলেন। তার কবিতা লেখার খাতা ছিটকে পড়ে জলে। ব্রজদা শিকারা চালানোয় বিশ্বরেকর্ড গতি সৃষ্টি করে খাতাটি উদ্ধার করে কবির হাতে দিয়ে বলেন, হ্রদের ওপর যেসব হাঁসের পাল উড়ে আসছে, তাদের নিয়ে কবিতা লিখতে। এই হচ্ছে আসল গল্প।
কিন্তু, ব্রজদার আক্ষেপ, ব্রজদাকে বাঙালি চিনলই না। এমন আরও নানা গুল্পে ব্রজদা মাতিয়ে রাখতেন সহকর্মীদের। কখনো এভারেস্টে বারো ফুট লাফ দিয়ে রাধানাথ শিকদারকে উচ্চতা গণনায় সাহায্য করছেন, আবার কখনো এমন এক বাঘের গল্প বলছেন, যে কিনা বেছে বেছে ধোপানীদের হাত খেয়ে যেত, আবার কখনো ক্রিকেট খেলায় ব্রজদা এমন শট মারেন যে বল অর্ধেক হয়ে গিয়ে একখণ্ড ফিল্ডারের হাতে পড়ে, একখণ্ড বাউন্ডারি পার হয়ে চলে যায়।
১৯৭৯ সালে পীযূষ বসুর পরিচালনায় ‘ব্রজবুলি’ চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়। ব্রজদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। অভিনয়ের আগে আনন্দবাজারের অফিসে এসে স্টাডি করেছিলেন বাস্তবের ব্রজরঞ্জন রায়কে। এমনই সব নানা গল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ব্রজদাকে নিয়ে, বইয়ে এবং বইয়ের বাইরেও।

মেসবাড়ি, অফিসঘর থেকে আড্ডার স্থল এবার সোজা পাড়ার রোয়াক। মধ্য কলকাতার অলিগলি, তস্য গলি পেরিয়ে ১৮ নম্বর পটলডাঙা স্ট্রিটের ঠিকানায় গেলেই সেই রোয়াক। মুখুজ্জেদের রোয়াক থেকে গল্পের খাতিরে যাকে চাটুজ্জ্যেদের রোয়াক নাম দিয়েছিলেন টেনিদার স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। টেনিদাকে নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস ‘চারমূর্তি’ ১৯৫৭ সালে ‘শিশুসাথী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে বই আকারে প্রকাশিত হয় অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে।
দ্বিতীয় উপন্যাস ‘চারমূর্তির অভিযান’ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। তবে গল্পেগুলোর সময়কাল সঠিক জানা যায় না। ঘনাদা বা ব্রজদাদের কাহিনী যেমন একেবারেই তাদের বোলচালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে, টেনিদাকে কিন্তু গল্প করার বাইরে নানা অ্যাদভেঞ্চারেও জড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। বিশেষত, টেনিদাকে নিয়ে লেখা পাঁচটি উপন্যাসের কাহিনী এই রকের আড্ডা মেজাজ থেকে বেরিয়ে আসা।
উপন্যাসগুলোতে টেনিদা ও তার দলবল কখনো কখনো জড়িয়ে পড়েছেন অসাধু জগতের মোকাবিলায়। গল্পগুলোতেও অনেক সময়েই পাওয়া গেছে নতুন ভেঞ্চারের স্বাদ। এখান থেকেই বোঝা যায়, টেনিদাকে আসলে কিশোরপাঠ্য চরিত্র করেই গড়তে চেয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যে কিনা সবসময় আড্ডা মেরে আর শাকরেদদের পয়সায় ডালমুট-পাঁঠার ঘুগনি খেয়েই কাটায় না, বীরবিক্রমে বেরিয়ে পড়ে অ্যাডভেঞ্চারেও। কিশোরমন যেমন আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না, তেমনই আরকী।

গল্পে টেনিদার আসল নাম ছিল ভজহরি মুখুজ্জে। আর তার তিন শাগরেদ হলেন ক্যাবলা (কুশল মিত্র), হাবুল (স্বর্ণেন্দু সেন) আর প্যালারাম (কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)। প্রতিটি দাদাদের গল্পেই যেমন একজন করে কথক রয়েছেন, এখানেও তেমনি কথক প্যালারাম। টেনিদাকে নারায়ণ গড়েছিলেন তার বাড়িওয়ালার আদলে। তারও ডাকনাম ছিল টেনিদা, এবং চেহারাও ছিল সুঠাম, শালপ্রাংশু। সেই টেনিদার নাম ছিল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা ২০ নম্বর পটলডাঙা স্ট্রিট। ঘনাদা, ব্রজদাদের কথা শুনলেই মনে হবে, তারা মধ্যবয়সী, কিন্তু টেনিদা সেখানে বহুবারের চেষ্টায় স্কুলপাশ এক তরুণ।
বয়সের সাথে তাল রেখেই হয়তো টেনিদার গপ্পোগুলোর মেজাজ হতো একেবারেই ছেলেমানুষী, কিন্তু হাস্যরসের মুন্সিয়ানার কমতি সেখানে ছিল না। সেখানে কখনো কাক এসে দুই ভাইয়ের ঝগড়া মেটাচ্ছে, কখনো টক আমের জন্য টেনিদার মামার চাকরি হচ্ছে, কখনো টেনিদার কুট্টিমামা ভালুকের নাক পুড়িয়ে দিচ্ছেন আবার কখনো একাই একটা ফুটবল ম্যাচে বত্রিশ গোল দিচ্ছেন টেনিদা। এই টেনিদা আবার যুদ্ধও করে এসেছেন বর্মার আরাকানের পাহাড়ে। তার নাক ডাকার ফায়দা তুলে জাপানিদের কাত করেছেন। আবার ক্যামোফ্লেজ ধরে পালাতেও সক্ষম হয়েছেন। কালিম্পঙের পাহাড়ে দেখা পেয়েছেন ইয়েতিরও। ইয়েতির কথা বলতে গিয়ে টেনিদাকে দেখা যায় ঘনাদার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে- ‘ঘনাদা। তিনি তো মহাপুরুষ। ইয়েতি কেন- তার দাদামশাইয়ের সঙ্গেও তিনি চা-বিস্কুট খেতে পারেন।’ হাস্যরসের আড়ালেও অগ্রজকে মান্যতা দেওয়ার মূল্যবোধ।
টেনিদার কাহিনী ‘চারমূর্তি’ থেকে একই নামে মুক্তি পাওয়া বিখ্যাত সিনেমাটিতে টেনিদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সদ্যপ্রয়াত অভিনেতা চিন্ময় রায়। রোয়াকে বসে ক্যাবলা-প্যালাদের পয়সায় কেনা তেলেভাজা বা চানাচুর খেতে খেতে এমন গপ্পো ঝাড়া টেনিদাই আবার বিপদের সময় হয়ে উঠতেন তার শাগরেদদের বলভরসা। ‘কম্বল নিরুদ্দেশ’ উপন্যাসে চোরাকারবারিদের ডেরায় গিয়ে পড়ার পর দশাসই চেহারার খগেন মাশ্চটককে টেনিদা ক্যারাটে আর জুডোর প্যাঁচে একাই ঘায়েল করে ফেলেন। সব মিলিয়ে টেনিদা খাদ্যরসিক অথচ নির্ভীক বাঙালি সমাজের পারফেক্ট আইকন তো বটেই।

অনেকটা টেনিদার ধাঁচেরই আরেকটি দাদা চরিত্র স্থান করে নিয়েছে বাংলাসাহিত্যে, তবে অত জনপ্রিয় হননি সেই দাদা। তিনি পিনডিদা। সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এই চরিত্রটি অবশ্য কলকাত্তাইয়া নন, বর্ধমানি। পুরো নাম প্রদীপ নারায়ণ দত্ত। সংক্ষেপে পিএনডি বলে তাকে ডাকত ব্রাজিলের ফুটবল ভক্তরা। পিএনডি থেকে পিনডিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন চ্যালাদের কাছে। পিনডিদা নাকি ব্রাজিলের নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তারপর হাঁটুর মালাইচাকি ঘুরে যাওয়ায় খেলার ক্যারিয়ারে ইতি। কোচ হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর সকল ভক্তকে কাঁদিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসেন।
টেনিদার মতো এই পিনডিদাও চ্যালাদের মাথায় চাঁটি মেরে খাবার আনাতেন। সেইসব চ্যালারা, অর্থাৎ কেবলু, হাবুল, চটপটি, কার্তিক আর সোনা সময়ে সময়ে চটেও যেত লিডারের ওপর। বিশেষত, পড়াশোনায় তুখোড় ও পিনডিদাকে বুদ্ধিতে টক্কর দেওয়া সোনা। কিন্তু বিপদের সময় এলেই বোঝা যেত আসল নেতা কে। পিনডিদাদের আড্ডা বসত খেলার মাঠে। একটি উঁচু ঢিপিতে বসতেন পিনডিদা, আর চ্যালারা মাটিতে। এনাদের আড্ডার বৈশিষ্ট্য ছিল, পিনডিদা মাঝেমাঝেই তাদের নানা বুদ্ধির খেলায় ফাঁসাতেন আর বাজি ধরতেন। বলা বাহুল্য, প্রতিবারই শাগরেদদের হার হতো।
টেনিদাদের মতোই পিনডিদারাও এই আড্ডার খোলস ছেড়ে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়তেন অ্যাডভেঞ্চারে। জমিদারবাড়ির হীরেচুরি ও জোড়াখুনের রহস্য ফাঁস করা এবং দেওঘরে গিয়ে সমস্ত অপরাধের নায়ক ডাকাত রাম বাদশার দলকে হাতেনাতে পাকড়াও করা সবই সম্ভব হয়েছিল পিনডিদার দুর্দান্ত বুদ্ধির জোরে। কিন্তু বাকি ‘হেভিওয়েট’ দাদাদের ক্যারিশমার কাছে পিনডিদা কিঞ্চিৎ আড়ালেই থেকে গেলেন।
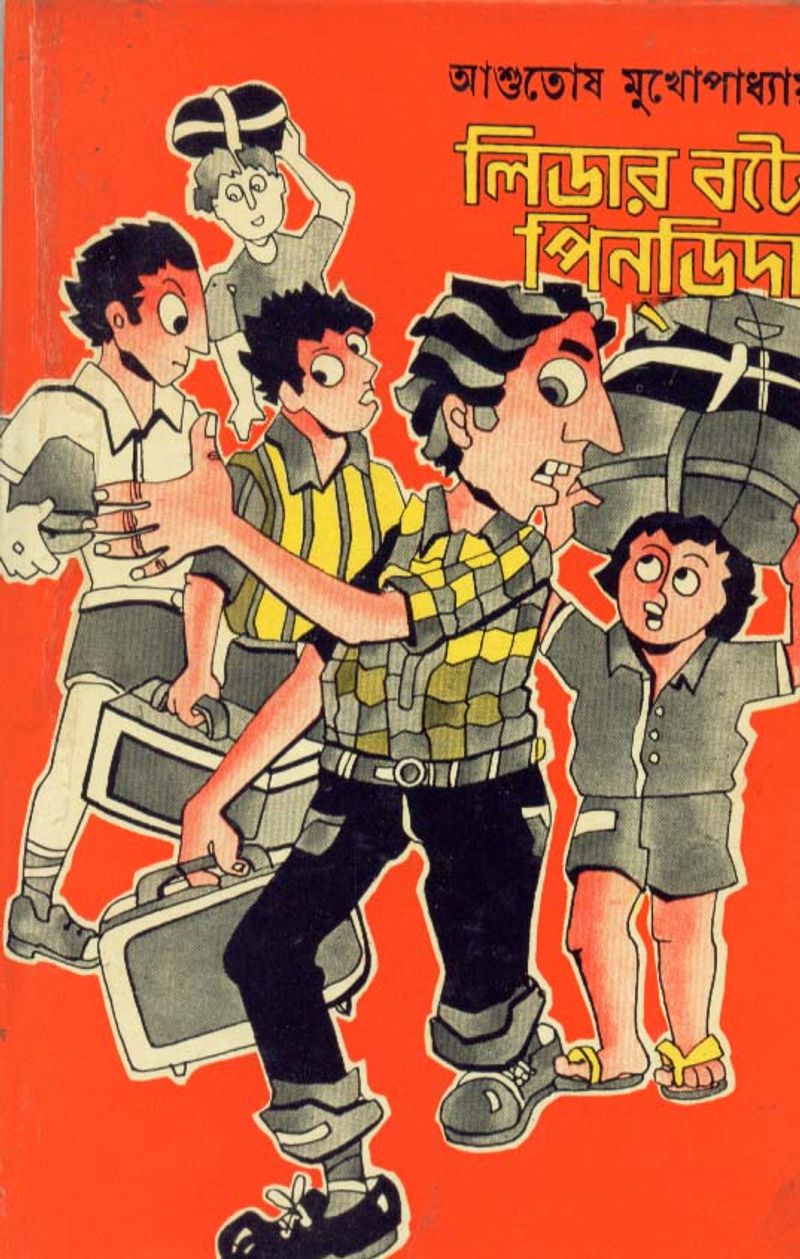
একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো, এইসব দাদারা কিন্তু উঠে এসেছিলেন সাধারণ রোজকার আড্ডা থেকেই। বনেদিয়ানায় মোড়া বৈঠকী আড্ডার পরিবেশ থেকে নয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই দাদারা, তাই হয়ত তাদের মধ্যে অগাধ দেশভক্তির নমুনা খুবই সাধারণ। কৌতূকপূর্ণ ভঙ্গিতে সে কথা উপস্থাপিত হলেও দেশের জন্য, সর্বোপরি মানুষের মঙ্গলার্থে কাজ করছি, এই বোধটা খুবই কাজ করত। হয়ত তাদের সময়ে তখনো রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসার লড়াইটা প্রকট হয়নি বলেই তারা কেবলমাত্র সামাজিক তাগিদ থেকেই মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে ব্রতী করতে চেয়েছিলেন।
টেনিদার কথাই ধরা যাক। ‘চারমূর্তির অভিযান’ উপন্যাসে আমরা জানতে পারছি, বস্তিতে আগুন লেগে গেলে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগেই একটি বাচ্চাকে উদ্ধার করে এনেছিলেন টেনিদা, টাইফয়েডে মুমূর্ষু হাবুলকে সেবা করে প্রায় বাঁচিয়ে তুলেছিলেন ওই টেনিদাই। টেনিদাদের প্রজন্ম আজ বহুদিন হারিয়ে গিয়েছে। তবু রয়ে গেছে তাদের আনন্দধ্বনি ‘ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস, ইয়াক, ইয়াক।’
এরা কয়েকজন ছাড়াও আরও অজস্র দাদাদের কাহিনীর ভিড়ে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের কেউ কেউ এমনই আড্ডাবাজ, রসিক আবার কেউ কেউ অত্যন্ত সিরিয়াস, কিন্তু আনন্দ দিতে সকলেই সফল হয়েছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুনদা, মেজদা থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা, বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদা, অহিভূষণ মল্লিকের নোলেদা, নারায়ণ দেবনাথের কেল্টুদা, তালিকাটা দীর্ঘ। সবশেষে বলা যায়, পাড়ার দাদারা হয়ত লুপ্তপ্রায় প্রজাতির আওতায় চলে গেছেন, কিন্তু যতদিন বাঙালির মনে সমাজচেতনা থাকবে, যতদিন বাঙালি বুকসেলফেই খুঁজে পাবে তার সংস্কৃতিকে, ততদিন এই দাদারা অন্তত হারিয়ে যাবেন না।


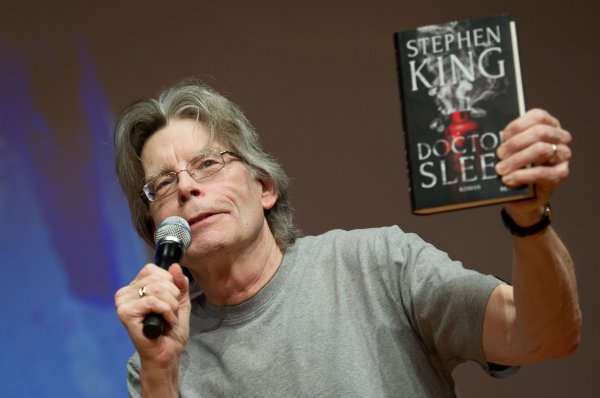



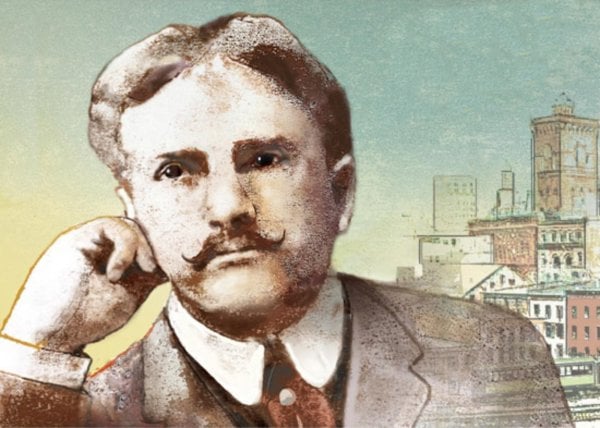

.jpg?w=600)